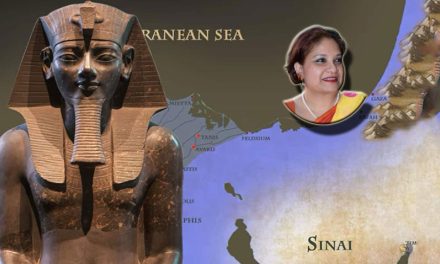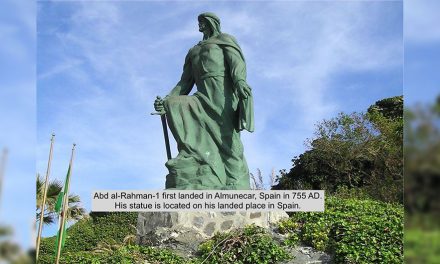কবি রহিমুন্নেসা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এই মহিলা কবির সময়কাল (আবির্ভাবকাল) ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ নির্ধারণ করেন এবং বাংলা একাডেমী পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৩৮৬ সালে (বাংলা) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কবি দৌলত উজির বাহরাম খা বিরচিত লাইলী মজনু কাব্যের পান্ডুলিপির শেষে অনুলেখিকা রহিমুন্নেসার আরেকটি আত্মপরিচিতির সন্ধান পান। (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি শ্রীমতী রহিমুন্নেসার আত্মপরিচিতি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৬৮ বাংলা, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৮)।
বলা হয় যে, রহিমুন্নেসার আদিপুরুষ ছিলেন কোরেশ বংশের লোক। কারবালা যুদ্ধের পর তাদের পূর্বপুরুষ কেউ কেউ বাগদাদে চলে যান। বাগদাদ থেকে তার পূর্বপুরুষ চলে আসেন মুংগেরে। সেখানে ইংরেজ মুসলমান সংঘটিত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে ইংরেজরা মুসলমানদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। এ সময় রহিমুন্নেসার পিতামহ চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার শুলকবহর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এতদঞ্চলে তিনি জংলী শাহ নামে খ্যাত হন। এই জংলী শাহের পুত্র আবদুল কাদির ছিলেন রহিমুন্নেসার পিতা। আবদুল কাদিরের তিন পুত্র আবদুল জাব্বার, আবদুস সাত্তার, আবদুল গফুর ও কন্যা রহিমুন্নেসা। নিতান্ত শৈশবেই রহিমুন্নেসা পিতৃহারা হন। এ সময় তার মাতা তার লেখাপড়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় রহিমুন্নেসার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল গফুরও মারা যান। ভাতৃশোকে বিহ্বল রহিমুন্নেসা এ সময় ভাতৃবিলাপ রচনা করেছিলেন। পরে নিজ কন্যা দোরদানা বেগমের মৃত্যুতে শোকাকুল হযছে তিনি ‘দোরদানা বিলাপ’ শোককাব্য রচনা করেন। রহিমুন্নেসার কবরের প্রস্তরফলকে বিদ্যমান সন-তারিখ অনুযায়ী তার জন্মসাল ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ১৯১৫। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। রহিমুন্নেসার শ্বশুরবাড়ি হাটহাজারী থানার মেখল গ্রামে। তার দাদাশ্বশুরের নাম গোলামু হোসেন, শ্বশুর জান আলী, স্বামী আহমদ আলী। তারা সেখানকার পুরুষানুক্রমিক জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত শেখ বংশের লোক। রহিমুন্নেসার স্বামীর কবরের প্রস্তফলকে বিদ্যমান তারিখ অনুযায়ী মৃত্যু ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ। স্বামীর পরলোকগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত রহিমুন্নেসার সাহিত্যচর্চার পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে রহিমুন্নেসার সাহিত্যচর্চা উনবিংশ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কবি রহিমুন্নেসার আদর্শ ছিল কবি দৌলত উজির বাহরাম খা ও আলাউল। তিনি যথাক্রমে তাদের লাইলী মজনু ও পদ্মাবতী কাব্যের পান্ডুলিপি নিজ হাতে তৈরি করেন। আমরা এটুকু জানি যে, উনবিংশ শতকে চট্টলায়প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গোটা থানায় দু-একটির বেশি ছিল না। রহিমুন্নেসা গৃহশিক্ষকের কাছে কিঞ্চিত বাংলা শিখেছিলেন। রহিমুন্নেসার লিপি ও ভাষাশৈলী প্রাচীন বাংলা লিপি ও সাহিত্যের অনুসারী।
ওপরে আমরা যে রহিমুন্নেসার পরিচয় পেলাম, সেটি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আবিষ্কৃত দৌলত উজির বাহরাম খা বিরচিত লাইলী মজনু কাব্যের পান্ডুলিপি শেষে অনুলেখিকা রহিমুন্নেসার দেয়া আত্মপরিচিতি অনুযায়ী। এখানে স্বয়ং রহিমুন্নেসা লিখেছেন-
মোর তিন ভ্রাতা আর মাত্রি গুণবতী/যৎকিঞ্চিত শাস্ত্রপাঠ সিখাইল নিতি ॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই নাম শুন তার/আবদুল জব্বার আর আবদুস ছত্তার ॥
মোহর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই নাম তান। আবদুল গফার করি অবোধ অংগান।
কূটবুদ্ধিহিনা। তিনি মাতার নাম। আলিম নিচা করি গুণে অনুপাম ॥…
এখানে দেখা যাচ্ছে আত্মপরিচিতিতে রহিমুন্নেসার জন্মসাল উল্লেখ নেই। রহিমুন্নেসা তার নামের আগে শ্রীমতী পদবি ব্যবহার করেছেন।
‘স্বামী আড্ডা শিরে পালি লিখিও ভারতী।
রহিমুন্নেসা নাম জান আদ্যে শ্রীমতী।’
অবশ্য তার এই পদবি ব্যবহারের কারণ জানা যায় না। কেবল নিজের নামেই নয়, তিনি তার মাতার নামের আগেও শ্রীমতী যুক্ত করেছেন।
‘প্রভু ভক্তা সতীত্ববর্তী জননী অনুপাম। শ্রীমতী আলিমন্নিচা জান তার নাম॥ তবে তার ধর্মে বিশ্বাস যথেষ্ট গভীর ছিল। তিনি বলছেন স্ত্রী জাতি হিন মুক্তি নাই সুবেবার। নবীর চরণ বিনে নাহক নিস্তার।’
রহিমুন্নেসা কবি, সুশিক্ষিতা ও মর্যাদাসম্পন্ন নারী ছিলেন। তবে নবপ্রবর্তিত বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারার সঙ্গে তাদের কোনো পরিচিতি ছিল না। তবে এ ক্ষেত্রে কেবল রহিমুন্নেসা নন, প্রথম মহাযুদ্ধকাল অবধি বাঙালি মুসলমান প্রায় সব কবিই প্রাচীন ধারার অনুসারী ছিলেন। এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও আমরা রহিমুন্নেসাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সূচনালগ্নের একজন কবি হিসেবে অত্যন্ত মর্যাদাসহকারে ধারণ করব।