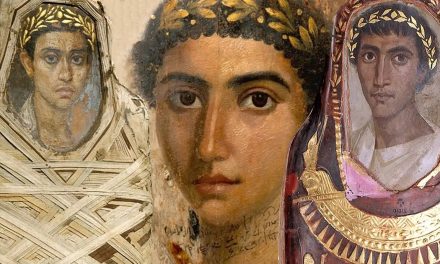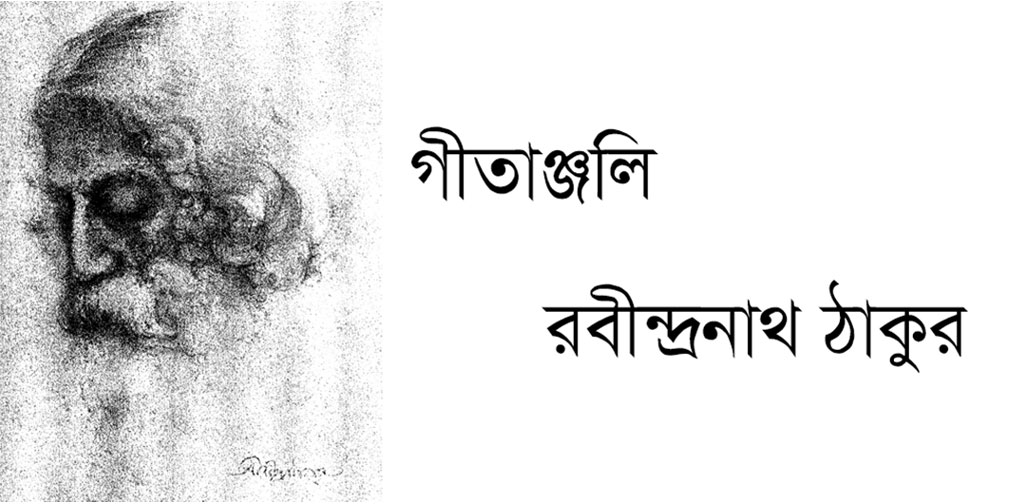
গীতাঞ্জলির একশো তিনটি কবিতার জন্য একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার- গীতাঞ্জলি তৈরির পিছনেও কিন্তু একশোটা গল্প আছে। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে বিদেশ যাওয়ার জন্য জাহাজ চড়বার দিনে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর তাই বিশ্রাম করতে গেলেন শিলাইদহে। সেখানে বসেই গীতাঞ্জলির কবিতা ইংরেজিতে তর্জমা করতে শুরু করলেন। এরপর ২৭শে মে, ১৯১২ তে যখন বিলেত পাড়ি দিলেন তখন সঙ্গে সেই তর্জমার খাতা। কিছু অনুবাদ জাহাজেও করলেন। এইসব অনুবাদের খাতাই তিনি অবনীন্দ্রনাথের বন্ধু ইংরেজ কলা শিক্ষক উইলিয়ম রোদেনস্টাইন এর হাতে সমর্পন করলেন।

রোদেনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তারই তিনটি কপি করে রোটেইনস্টাইন অভিমতের জন্য পাঠিয়ে দিলেন কবি Yeats, Bradley , Stopford Broke এর কাছে। ইংল্যান্ড থেকে ১৯১৩ তে কবিগুরু এক চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে জানাচ্ছেন – “গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা লিখেছিস। ওটা যে কেমন করে লিখলাম এবং কেমন করে লোকের এত ভালো লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। গেল বার যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোল আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেইজন্যে ঐ গীতাঞ্জলির কবিতা গুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুম। একটা ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি পকেটে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখনি উসখুস করে উঠবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জমা করতে বসব। আর ঘটলও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছান গেল। রোটেইনস্টাইন আমার কবিযশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথা প্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তার হাতে আমার খাতাটি সমর্পন করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি Yeats এর কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন। তারপর কি হলো সে ইতিহাস তোদের জানা আছে।”

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর, ১৯১৫
বারবার কবির মনে হয়েছে এ তার আত্ম নিবেদনের কবিতা। প্রতিটি কবিতাই যেন তার নৈবেদ্য আর নিবেদন – ” এই কবিতাগুলি আমি লিখব বলে লিখিনি – এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন– এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।” গীতাঞ্জলি যেন প্রাণের দেবতার সাথে কবির এক নিভৃত আলাপ – পবিত্র গভীর রহস্যময় কিন্তু অশ্রুত নয়, সুর মূর্ছিত। সে সুরের গৌরব অলঙ্কার ভারে জর্জরিত নয়, বরং নিরাভরণ সরলতায় পূর্ন। এক ব্যাপ্ত, বিপুল ‘তুমি’র সাথে যেন তৈরি হলো এক নাটকীয় সন্ধি। কবি তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে যথেষ্ট বিনয়ী ও ছিলেন। কবির কথায় – ” যতদিন আমার গীতাঞ্জলির খাতা পূর্ন হয়নি ততদিন আমি বারবার চেষ্টা করেও দেশ ছেড়ে বেরোতে পারিনি। আমি কতবার মনে করেছি এবং তোমাদেরও বলেছি, বাংলা ভাষাতেও এগুলো ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয় – এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা – নিতান্তই নিরলঙ্কার। এখন মনে হচ্ছে কেবলমাত্র নিজের জন্য লিখলেই সেটা যথার্থ সকলের জন্য লেখা হয় – এবং অলঙ্কারটা বাদ দিলেই মুল্যটা বেড়ে ওঠে।দেখতে পাচ্ছি গীতাঞ্জলি তাকে দেওয়া হয়েছিল বলেই সকলকে দেওয়া হয়েছে।”

লন্ডনে রেলস্টেশন, ১৯১২
অনেকেই হয়তো জানেন না, ১৯১২ সালের ১৬ জুন লন্ডনে রেলস্টেশন থেকে হোটেলে যাওয়ার পথে ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। অনেক চেষ্টার পর সেই পাণ্ডুলিপি ফেলে যাওয়া মালামালের অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথের লেখায় পাই , “… আমরা লন্ডনে এসে পৌছালাম এক সন্ধ্যায়।চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে এসে জানা গেল টমাস কুক আমাদের জন্য ব্লুমসবেরি অঞ্চলে একটি হোটেলের কয়েকটি কামরা ভাড়া করে রেখেছেন। স্টেশন থেকে টিউব রেল যোগে আমরা ব্লুমসবেরি অভিমুখে রওনা দিলাম।মাটির তলায় সুড়ঙ্গ রেলপথে এই আমার প্রথম অভিযান। নতুন অভিজ্ঞতার জন্যই হোক কিংবা অত্যধিক দায়িত্ব ভারের জন্যই হোক – আমি নিজের হাতে অতি সন্তর্পনে বাবার যে সুটকেসটি বহন করে আনছিলাম, টিউব রেল থেকে নামবার মুখে সেইটিই নামাতে ভুলে গেলাম। এই সুটকেসের মধ্যেই বাবার ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ও আরো অনেক সব দরকারি কাগজপত্র ছিল। পরেরদিন বাবা যখন রোটেইনস্টাইনের বাড়ি যাবেন, সুটকেসের খোঁজ পড়ল, আর তখনই বোঝা গেল সেটি টিউবে ফেলে আসা হয়েছে। আমার অবস্থা অনুমেয়, শুকনো মুখে আমি চলে গেলাম টিউব রেলের লস্ট প্রপার্টি অফিসে। সেখানে যেতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হারানো ধন ফেরত পাওয়ার পর আমার প্রাণে যে কি গভীর স্বস্তি হয়েছিল – সে আমি কখনো ভুলবো না । মাঝে মাঝে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ভাবি, যদি ইংরেজি গীতাঞ্জলি আমার অমনোযোগ ও গাফিলতির দরুন, সত্যিই হারিয়ে যেত তা হলে …”

গীতাঞ্জলির কাভার পেজ, ১৯১৩
ভাগ্যিস সেটি পাওয়া গিয়েছিল। নইলে বাঙালি লেখক-কবির কপালে নোবেল অধরাই থেকে যেত। অবশেষে ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর রোটেনস্টাইনের উৎসাহে ইংরেজিতে ‘সং অফারিংস’ নামে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে মাত্র সাড়ে সাতশ কপি বই প্রকাশ করা হয়। ১৯১৩ সালের মার্চে ম্যাকমিলান বইটি প্রকাশ করলে নোবেল পাওয়ার আগেই বইটির ১০টি সংস্করণ বের হয়।আর প্রকাশের পরেই গীতাঞ্জলি হয়ে উঠলো দেশ কালের সীমানা ছাড়ানো মানুষের আপন গান – তৈরি হলো আপামর বাঙালি তথা ভারতবাসীর মহাকাব্যিক ইতিহাস!!
তথ্যসূত্র –
1) গীতাঞ্জলি – বিশ্বকবির নোবেল প্রাপ্তির ১০০ বছর – তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ , পশ্চিমবঙ্গ সরকার
2) পিতৃস্মৃতি – রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3) গীতাঞ্জলি – পৌষ উৎসব ১৪১৭