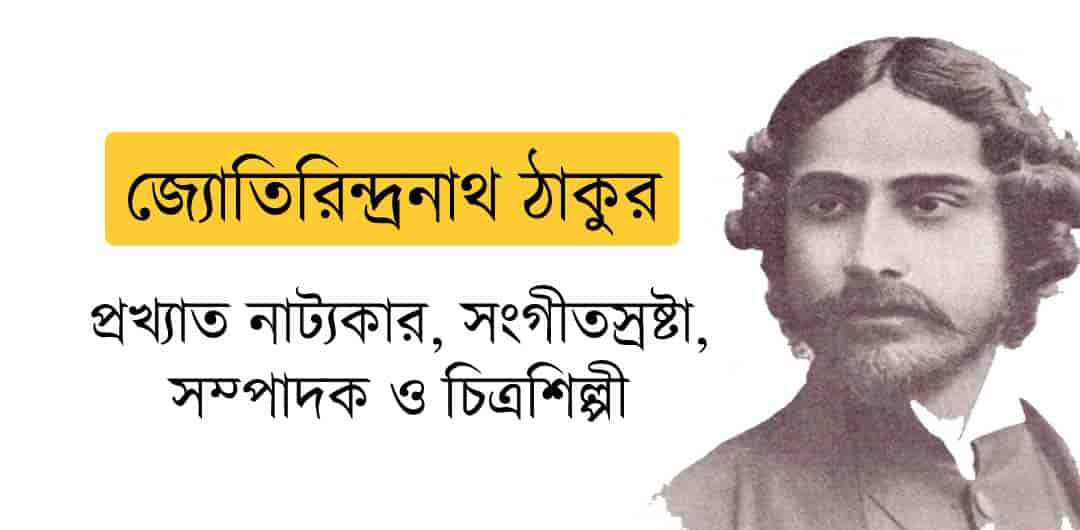
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর না থাকলে বাঙালি গীতা-রহস্যের হদিশ পেত না। সংস্কৃত নাটকের বিপুল ভাণ্ডার অধরাই থেকে যেত। বঞ্চিত থাকত পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস আস্বাদন থেকে। গিরিশ ঘোষের আগে বঙ্গ রঙ্গালয়ের জনপ্রিয়তাকে তিনিই গড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে বাঙালি স্বদেশিয়ানার প্রথম পাঠ নিয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষের হাত ধরে বিপ্লবী যুগ শুরু হওয়ার অনেক আগে তিনিই প্রথম বাঙালিকে ‘গুপ্ত সমিতি’ গড়তে শিখিয়ে ছিলেন ‘হামচুপামুহাফ’ গঠনের মধ্য দিয়ে। নিজের অন্তঃপুরিকা স্ত্রী কাদম্বরীকে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনসে ঘোড়া ছুটিয়ে নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন। বাঙালিও যে চাইলে ব্যবসা করে প্রতিপক্ষ ইংরেজ ব্যবসাদারদের পাততাড়ি গোটানোর ব্যবস্থা করতে পারে, তাও প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি। বিদ্বজ্জন সমাগম, সঞ্জীবনী সভা, সারস্বত সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যসেবার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে গড়ে দিয়েছিলেন বাঙালির গর্বের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
লেখাপড়ায় ‘বিষম বিতৃষ্ণা’—-
রবীন্দ্রনাথের ‘জ্যোতিদাদা’, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর ‘নতুন’ ও ইন্দিরা দেবীর ‘নতুন কা’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম ৪ মে, ১৮৪৯ সালের মধ্যরাতে (২২ বৈশাখ, ১২৫৬)। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাদেবীর পঞ্চম পুত্র। সে ছিল এমন এক সময়, যখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশের বিত্ত ও বৈভবে টান পড়েনি। মুঘল ও ইংরেজ সংস্কৃতি মিলেমিশে ছিল সাধারণ ভারতীয়দের জীবনে। আবার তাঁর জন্মের সাত মাস পরে ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৯, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ-সহ ২১ জন ভক্তবন্ধুকে নিয়ে বিধিমতো প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সেও এক সন্ধিক্ষণ।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবের দিন শুরু হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব জাঁকিয়ে বসার আগে। তাঁর বাল্যস্মৃতিতে ঠাকুরবাড়িতে দেখা দুর্গোৎসবের উল্লেখ আছে। যদিও সেই পুজোর দিনগুলোয় দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় থাকতেন না। উৎসবের ভার সামলাতেন তাঁর দুই ভাই গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স যখন ১০, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে লক্ষ্মী-জনার্দন শিলার নিত্যপূজা ও দুর্গোৎসব বন্ধ করে দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায়, “আমাদের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপ ব্রহ্মমণ্ডপে পরিণত হল।” গিরীন্দ্রনাথের পরিবার আলাদা হয়ে দ্বারকনাথের বৈঠকখানা বাড়িতে (৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) পূজাপাঠের ব্যবস্থা করলেন। দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ভদ্রাসন বা মূল বাড়িতে (৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) উঠে এলেন। গিরীন্দ্রনাথের পরিবারে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি সব ধরনের হিন্দু পৌত্তলিক রীতিনীতি পালিত হত।

ত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দাঁড়িয়ে), বামে তার স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বসে), পাশে ডানে তার স্ত্রী কাদম্বরী দেবী
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদালানের যে পাঠশালায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়, সেখানকার ‘গুরুমশায়টি ছিলেন সেকেলে পণ্ডিতের জ্বলন্ত আদর্শ। রং কালো, গোঁফজোড়া কাঁচাপাকায় মিশ্রিত মুড়া-খ্যাংড়ার ন্যায়। চুল লম্বা, ওড়িয়াদের মতো পিছন দিকে গ্রন্থিবদ্ধ।’ তিনি কখনও হাসতেন না। কেবল ছাত্রদের বেত দিয়ে মারার সময়ে ‘বর্ষণোন্মুখ শ্রাবণমেঘে বিজুলিলেখার মতো’ তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠত। সেই বেতের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ সেটি লুকিয়ে ফেলেন। ফলে গুরুমশায় ‘বৎসহারা গাভীর মতো’ শোকে অধীর হয়ে পড়েন।
কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে অমিত শাহকে চিঠি শোভনের, ইমেলে
অভিযোগ সিপিকেও—
এর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের কাছে। তিনি খুবই কড়া ধাতের মাস্টার ছিলেন। খেলার সময় তাঁর কাছে ছিল অবান্তর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে হত ‘তিনি যেন জেলখানায় আছেন— সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট অন্ধকার। মুক্তির জন্য তাঁহার প্রাণ ছটফট করিত।’ এর ফলে তাঁর লেখাপড়ার উপরে ‘বিষম বিতৃষ্ণা’ তৈরি হয়েছিল। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বলা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়তে পড়তে এই পরিবেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতিকে। এবং বোঝা যায়, কেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে ‘সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালোমন্দর মধ্য দিয়া’ তাঁর ‘আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে’ ছেড়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।
আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ বিশেষ ছাপ ফেলেছিলেন। এঁরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এক দিকে যেমন ব্যায়াম, কুস্তি, সাঁতার শিখতে উৎসাহিত করেন, তেমনই নাট্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞানশিক্ষা, ভাষাশিক্ষা ইত্যাদির দিকেও ঠেলে দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায়, “ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে একটা জ্ঞানের ঢেউ এসেছিল; পিতৃদেবের জ্বলন্ত ব্যাখ্যান, মেজদাদার মনোহর ব্রহ্ম-সংগীত— বড়োদাদার গভীর তত্ত্ববিদ্যা ও অনুপম স্বপ্নপ্রয়াণ— জ্ঞানধর্মের আলোক বিস্তার করেছিল।” জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বড় হয়ে ওঠার পরিবেশটি বুঝতে অসুবিধে হয় না।
দাদার সঙ্গে মুম্বই পালানো—
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদালানে গুরুমশায়ের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার পরে সেন্ট পল্স স্কুল, মন্টেগুস অ্যাকাডেমি ও হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকার শুরু এই সময়ের ছাত্রজীবন থেকে। কিছুটা আকস্মিক ভাবে। তিনি হঠাৎই জীবনে প্রথম পোর্ট্রেট আঁকেন লর্ড সিনহার পিতৃব্য প্রতাপনারায়ণ সিংহের মণিরামপুরের বাড়িতে বসে। এর পরে হিন্দু স্কুলের ক্লাসে বসে শিক্ষক জয়গোপাল শেঠের ছবি এঁকেছিলেন নিজের খেয়ালে। এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কখনও পোর্ট্রেট আঁকেননি বা চেষ্টা করেননি। তাঁর এই ক্ষমতা পরে বুঝতে পারেন।
হিন্দু স্কুলের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভর্তি হন কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কলেজে। এখান থেকেই ১৮৬৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছু দিন পড়ার পরে তিনি আনুষ্ঠানিক ছাত্রজীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তারকনাথ পালিতের অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মুম্বই পালিয়ে যান (১৮৬৪)। তবে স্কুল ছাড়লেও পড়াশোনা তিনি কখনও ছাড়েননি। বরং নানা বিষয়ে তিনি ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকেন। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার অফুরান জগতের সন্ধান পান।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খুব অল্প দিনের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র শিখে বাজাতে শুরু করেন। সঙ্গীতের জগতে তাঁর প্রবেশ ঘটতে থাকে। তাঁর বাজানো সেতার, হারমোনিয়াম বা পিয়ানো শুনে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। ব্রাহ্মসমাজে গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজানোর ভার দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়। তবে তিনি জানিয়েছেন, “হার্মোনিয়াম প্রবর্তনের পূর্বে সমাজে বিষ্ণুবাবুর (চক্রবর্তী) গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন হিন্দুস্থানি সারেঙ্গ বাজাইত। এই মান্নার মতো নিপুণ সারেঙ্গি কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না।” মান্না নাকি বাড়িতে সর্বদা সারা গায়ে সাপ ছড়িয়ে বসে থাকতেন।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতেন। ১৯৬৮ সালের জুনে কর্মসূত্রে তিনি ‘বোম্বাই’ চলে গেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতে শুরু করেন। রামমোহন রায় যে ধর্মের সূচনা করেছিলেন, তার বীজ বাঙালি তথা ভারতবর্ষীয় সমাজে রোপণ করতে দেবেন্দ্রনাথই প্রথম উদ্যোগ নেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, “তখন বড়ো বড়ো গায়কদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হইত।” এঁদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র রায় ও যদু ভট্টকে তিনি পেয়েছিলেন। এঁদের সাহচর্যে তিনিও ব্রহ্মসঙ্গীত লেখার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। তবে তিনি নিজে অপূর্ব সব ব্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা হলেও, মনে করেছেন তাঁদের পরই ‘রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবিপ্রতিভা এখন ব্রহ্মসংগীতকে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।’ রবীন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র সম্পর্কের এ এক আশ্চর্য দিক। রবীন্দ্রনাথের ‘মেন্টর’ যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।
লুচি-কচুরি খেতে খেতে নাট্যশালার ভাবনা—-
জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতলার ঘরে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর থেকে বারো বছরের ছোট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন কৈশোর ছাড়িয়ে পূর্ণ যৌবনে প্রবেশ করেছেন, শিশু রবি তাঁকে দেখেছিলেন অপার বিস্ময়ে, আরও অনেকের মতোই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রূপ ছিল দেখার মতো। একবার চোখের দেখা দেখবেন বলে রসরাজ অমৃতলাল বসু অপেক্ষা করে থাকতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগমনের আশায়। প্রতিভার দীপ্তি চেহারায় প্রকাশ পেত। রবীন্দ্রনাথের আগে দেবেন্দ্রনাথের সব থেকে সম্ভাবনাময় সন্তান ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।
১৮৬৭ সালে যখন ‘হিন্দুমেলা’র সূচনা হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আঠেরো বছরের নব্য যুবক। রূপ, যৌবন, ব্রাহ্মরুচি, তীব্র অনুসন্ধিৎসা আর জ্ঞানপিপাসা নিয়ে তিনি তখন বঙ্গসমাজকে আলোড়িত করতে উঠে আসছেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের পরিবেশ, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী, মধুসূদন দত্ত, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয় চৌধুরী, বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্টের মতো মানুষের সান্নিধ্য সেই দুরন্ত যুবককে যেমন পরিণতি দিয়েছিল, তেমনই হিন্দুমেলার উত্তেজনা তাঁর মানস গঠনে সাহায্য করেছিল। মাৎসিনি গ্যারিবল্ডির অনুপ্রেরণা, ইউরোপ জুড়ে জাতীয়তা আন্দোলন, ফরাসি সাহিত্য ও ইতিহাস তাঁকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। তাই এই সময়কালে আমরা তাঁকে দেখি সাহিত্য, চিত্রকলা, ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় মগ্ন থাকার পাশাপাশি নাটক ও অভিনয় নিয়েও মেতে থাকতে।
অবন ঠাকুরের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গী। দু’জনে মিলে ঠাকুরবাড়িতেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন একটি নাট্যদল। ‘জোড়াসাঁকো নাট্যশালা’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোলো। প্রথমেই মধুসূদনের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক অভিনীত হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা পান। ফলে বিপুল উৎসাহে শুরু হল নতুন নাটকের মহলা। নাটকের খোঁজ করতে তিনি ও আরও চার জন— কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মিলে গড়লেন ‘কমিটি অব ফাইভ’ বা ‘পঞ্চজন’ সমিতি। ছিল একটি ‘ইটিং ক্লাব’ও। সেখানে লুচি-কচুরি খেতে খেতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা গড়ার ভাবনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাথায় আসে।
দর্শকের ভয়ে মূর্ছা গেলেন স্ত্রী চরিত্রের পুরুষ অভিনেতারা—-
সেই নাট্যশালায় প্রথমে মধসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ অভিনীত হলেও সকলেই অনুভব করেন যে, বাংলা সাহিত্যে অভিনয় করার মতো নাটক বেশি নেই। এই অভাব দূর করতে বিদ্যাসাগরের নির্বাচন করে দেওয়া বিধবাবিবাহ, কৌলীন্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ বিষয় নিয়ে নাটক লিখতে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ নাটককে পুরস্কৃত করার কথাও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ভাল নাটক না পাওয়ায় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে ভার দেওয়া হয় নাটক লেখার। জোড়াসাঁকোয় সেই নাটক অভিনয়ের জন্য রিহার্সাল শুরু হয়।
কিন্তু নাটকের দিন (৫ জানুয়ারি ১৮৬৭) যে সব পুরুষ ‘স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিক পূর্বেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার ভয়ে সাজঘরে ঘন ঘন মূর্ছা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ির ডাক্তার দ্বারিকবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই খাড়া করিয়া তুলিলেন।’ তবে অক্ষয় চৌধুরী কিছুতেই সাহস করে দর্শকের সামনে আসতে পারেননি। তাঁকে বাদ দিয়েই নাটক মঞ্চস্থ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নটীর ভূমিকায় অভিনয় ও কনসার্টে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন। তিনি গানও গাইতেন। আর নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ অভিনয়শেষে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে “যারা পালট্ নাই, পালট্ (প্লট) নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক,” বলে আস্ফালন করেছিলেন।
স্বাদেশিকতা বোধের যে প্রচার ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করেছিলেন, তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ব্রাহ্মসমাজ হয়ে উঠেছিল স্বদেশি ভাবনার কেন্দ্রস্থল। জোড়াসাঁকোয় পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পর্দাপ্রথা থেকে মুক্তি ঘটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাড়ির মেয়েদের ইংরেজি গল্প-উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করে শোনাতে শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক ‘দীপনির্ব্বাণ’-এর লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টাতেই।
ন’বছরের কাদম্বরীকে পছন্দ করেননি দাদা-বৌদি—
১১ এপ্রিল, ১৮৬৮ সালে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে নবগোপাল মিত্রের অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা ‘উদ্বোধন’ লেখেন। তবে তাঁর কণ্ঠস্বরের তেমন জোর ছিল না বলে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাটি পাঠ করেন। ঠিক তার পরের মাসেই ৫ জুলাই ১৯ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা ন’বছরের কাদম্বরীর বিয়ে হয়। কিন্তু এই বিয়ে মেনে নিতে পারেননি সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। কারণ কাদম্বরীকে কারও পছন্দ হয়নি। এর প্রমাণ রয়েছে সেই সময়ে লেখা তাঁদের চিঠিপত্রে। তবে ন’বছরের বালিকাবধূকে ঘিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে নারী স্বাধীনতা নিয়ে তেমন কোনও আগ্রহ পরবর্তী চার বছরে ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ (১৮৭২) লেখা অবধি গড়ে ওঠেনি। তিনি তখন স্বদেশি ভাবনা নিয়েই বিভোর ছিলেন।
বৌদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী; Image source: Wikimedia
দেবেন্দ্রনাথের কারণেই যে তাঁর পুত্রদের মনে স্বদেশ চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই স্বদেশি তাঁত চালু করে, তাতে তৈরি গামছা মাথায় বেঁধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলায় নেচেছিলেন বলে জানিয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল। মালকোঁচা মেরে ধুতি আর মাথায় শোলার টুপির উপরে শিরস্ত্রাণ চাপিয়ে স্বদেশি পোশাক পরে কলকাতায় ঘুরে বেড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন। আত্মীয় বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রুক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।’
খুলির চোখের কোটরে বসানো হত দু’টি মোমবাতি—
এই পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ‘সঞ্জীবনী সভা’ স্থাপন। সাংকেতিক ভাষায় সেই সভার নামটির উচ্চারণ ছিল ‘হামচুপামুহাফ’। এই সভা স্থাপনের পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল ইতালির ‘কারবোনারি’ গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার ইতিবৃত্ত। সভার সদস্যরা গোপন স্থানে মিলিত হতেন ও নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কথা বলতেন। কারবোনারির সভ্যরা ইতালির স্বাধীনতা, সংযুক্তিকরণ ও গণতন্ত্রের জন্য কাজ করতেন। এই গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে ইতালির বিপ্লবী নেতা জুসেপ্পে মাৎসিনির যোগ ছিল। কলকাতার ঠনঠনিয়ায় এক পোড়ো বাড়িতে এই গুপ্ত সভা বসত। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথও সভ্যদের একজন ছিলেন। এই সভা যখন বসত, টেবিলে একটি মড়ার খুলি রাখা থাকত। খুলিটির চোখের কোটরে বসানো হত দু’টি মোমবাতি। খুলিটি মৃত ভারতবর্ষ ও মোমবাতি দু’টি ছিল ভারতের প্রাণ সঞ্চার ও জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তোলার সংকেত! সভা আরম্ভ হত বেদমন্ত্র পাঠ করে।
বন্ধুবান্ধব ও ভাইদের নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে শিকার করতে বেরোতেন, তার পিছনেও ছিল স্বদেশি বীররস চর্চার প্রয়াস। তাঁর নীল চাষ, পাট ও স্টিমারের ব্যবসায় নামাও ওই একই কারণে। স্বদেশি ব্যবসায়ী হিসেবে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে তিনি অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিলেন।
হিন্দুমেলা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। হামচুপামুহাফ গুপ্ত সমিতিও একদিন বন্ধ হয়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার প্রচারে গুপ্ত সভা ও মেলার অনুপস্থিতি পূরণ করেছিলেন নাটক লিখে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার সঙ্গে নাট্যকার হিসেবেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিষেক ঘটে। ১৮৭৪ সালে তিনি লেখেন ‘পুরুবিক্রম’ নাটক। যদিও এর আগে সনাতনপন্থী আদি ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ’। এই নতুন সমাজ স্ত্রী স্বাধীনতার উপরে জোর দেয়। ব্যাপারটা তখন অনেকের কাছে ‘কিঞ্চিৎ আতিশয্য’ বলে মনে হয়েছিল। সেই আতিশয্যের প্রতি কটাক্ষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন তাঁর প্রথম একাঙ্ক প্রহসন ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি আকৃষ্ট হন সত্যেন্দ্রনাথের বিদেশ থেকে ফিরে আসার পরে। নিজেই জানিয়েছেন, “সেজদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের পরিবর্তন ঘটিয়া ছিল। তখন হইতে আমি অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী নহি, বরং একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম।” তিনি লিখছেন, ‘আমি এত বড়ো পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোনও বাগানবাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তারপর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছাইয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত।’
তেতলার ঘরে টেবিল ঘিরে বসত আড্ডা—
এর পরে দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। কলকাতা ছেড়ে তাঁকে যেতে হয় কটক ও শিলাইদহে। এই পর্বেই তিনি লেখেন ‘পুরুবিক্রম’ নাটক। এতে সত্যেন্দ্রনাথের লেখা ‘মিলে সবে ভারতসন্তান’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘এক সূত্রে বাঁধিয়াছি’ গানগুলি যুক্ত করা হয়। পরের বছর ১৮৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লেখেন ‘সরোজিনী’ নাটকটি। যে নাটকের গান তৈরির সময়ে পিয়ানোয় তাঁর তোলা সুরে চোদ্দো বছরের রবীন্দ্রনাথ কথা জুড়ে তৈরি করেন ‘জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ/ পরাণ সঁপিবে বিধবাবালা’ গানটি। এই নাটকই যেমন নাট্যকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে চেনায়, তেমনই রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার ও গড়ে তোলার পর্বেরও সূচনা করে।
জোড়াসাঁকোর তেতলার ছাদের ঘরে তখন থাকতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী। ঘরের লাগোয়া লম্বা ছাদ। সেই ছাদে তৈরি করা হয়েছিল বাগান। ঘরে ছিল একটি গোল টেবিল। দেওয়ালের গায়ে পিয়ানো রাখা। সেই টেবিল ঘিরে বসতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, বালক রবীন্দ্রনাথ। এখানেই ‘সরোজিনী’ নাটক লিখতে লিখতে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করে তাঁকেও সেই সভায় স্থান দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এখানে অনেক ‘জ্যোৎস্নাময়ী মধুযামিনী’ কাটিয়ে ছিলেন তিন জনে। এই সভাতেই কাদম্বরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা বাড়ে। বিলেত থেকে ফিরে এই সভায় বসেই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করতে শুরু করেন তাঁর নিজের সুর। যাতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ছোঁয়া থাকলেও তা ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত। নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় তার চেহারা বদলে দেন রবীন্দ্রনাথ।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে সেই সভার অবদান যেমন অসীম, তেমনই এই সভাই রবীন্দ্রনাথকে ‘নব-ভানু’ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। প্রশান্তকুমার পালের কথায়, “কাদম্বরী দেবী নিরক্ষরা বা সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্বল করে শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করেছিলেন।” তাঁকে শিক্ষিত করে তুলতে ঠাকুরবাড়ির হিসেবের খাতায় ‘ধারাপাত’ কেনার উল্লেখ রয়েছে। ক্রমশ এই আপাত অশিক্ষিত “বালিকাটি কোন অবস্থা থেকে আপন অন্তর্নিহিত শক্তি ও পরিবেশের প্রভাবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই একটি সাহিত্যগোষ্ঠীর মক্ষীরাণীতে পরিণত হয়েছিলেন”, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। কিন্তু এই সাহিত্যগোষ্ঠীতে অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে স্থান দিলেও হয়তো কাদম্বরীর প্রতি উদাসীন থেকেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

কাদম্বরী দেবী
‘গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই’—-
‘সরোজিনী’র পরে ‘অশ্রুমতী’ (১৮৭৯) ও ‘স্বপ্নময়ী’ (১৮৮২)। তার পরেই মৌলিক নাটক লেখা থামিয়ে দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অমৃতলাল বসুকে জানিয়েছিলেন, “নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।” এ ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এক বিশেষ গুণ। তিনি তাঁর সীমা মাপতে জানতেন। নাটক ছেড়ে তিনি মেতে ওঠেন অনুবাদ কর্মে। সংস্কৃত, মরাঠি, ইংরেজি, ফরাসি থেকে অনুবাদ করতে শুরু করেন। অনুবাদেও ছাপ পড়েছে তাঁর সমাজচেতনার দিকটি। মলিয়ের, থিয়োফিল গোতিয়ের, ভিক্টর হুগো, ভলতেয়ার, মঁপাসা, এমিল জোলা প্রমুখের লেখা তিনি অনুবাদ করেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর অনুরোধে সংস্কৃত নাটক অনুবাদে হাত দেন। কালিদাস, শূদ্রক-সহ বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে সঙ্গে তিনি বাঙালির পরিচয় করিয়ে দেন। চার বছরে সতেরোটি নাটক অনুবাদ করেন। একটি ব্রহ্মদেশীয় নাটকও বাংলায় অনুবাদ করেন। শেষ জীবনে বাল গঙ্গাধর তিলকের ৮৭২ পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ ‘গীতা রহস্য’ বা ‘কর্মযোগশাস্ত্র’ অনুবাদ তাঁর জীবনের এক প্রধান কীর্তি।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর এক অক্ষয় কীর্তি বাংলায় আকারমাত্রিক স্বরলিপির সহজ পদ্ধতির আবিষ্কার। যা ছাপা ও পড়ার সুবিধে করে দিয়ে সঙ্গীত সাধনাকে মানুষের আয়ত্তে এনেছিল।—
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি ছদ্মবিজ্ঞান জানা ছিল। তা হল ‘ফ্রেনোলজি’ বা ‘শিরোমিতি-বিদ্যা’। মানুষের মাথার গড়ন পরীক্ষা করে তিনি তার মনের চলন বলতে পারতেন। মুখের ছবি আঁকার নেশা ছিল তাঁর। পরিবারের নানা সদস্য, বন্ধু, অভ্যাগতদের অজস্র প্রতিকৃতি এঁকেছেন, যা দেখলে অবাক হতে হয়। সে কালের অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি ফোটোগ্রাফে ধরা না পড়লেও, ধরা আছে তাঁর আঁকা ছবিতে। প্রায় ১৮০০ স্কেচ সংরক্ষিত আছে আজও। রবীন্দ্রনাথ ও রোদেনস্টাইনের উদ্যোগে ১৯১৪ সালে এই স্কেচগুলি নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়।
এমন আশ্চর্য গুণের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথের এই পঞ্চম পুত্রের জীবন হঠাৎই থমকে যায় ২০ এপ্রিল, ১৮৮৪ সালে। ঠাকুর পরিবারকে হতবাক করে দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ২৫ বছরের অভিমানী স্ত্রী কাদম্বরী দেবী আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন। যদিও সেই মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত ভাবে আজও জানা যায়নি। হয়তো কাদম্বরী তাঁর মৃত্যু দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘সৃষ্টিসুখের উল্লাসে’ মেতে থাকা জীবন থমকে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বংশের ভরকেন্দ্রটিতে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। দেখা গিয়েছে ১৮৮৪ সালের পরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ক্রমশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। বিবাহিত রবীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন শিলাইদহ হয়ে শান্তিনিকেতনে। দ্বিজেন্দ্রনাথও বাসা বেঁধেছিলেন সেখানে। সত্যেন্দ্রনাথ গেলেন বালিগঞ্জের গুরুসদয় দত্ত রোডের বাড়িতে। হেমেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। বীরেন্দ্রনাথের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল। ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারপাশ ফাঁকা হয়ে গেল। ১৮৯৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘ভারত সঙ্গীত সমাজ’-এর কাজকর্ম কমে যাওয়ায় তিনি জনজীবন থেকে অবসর নেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাপ্রাঙ্গন; Image source: Wikimedia
১৯০৮ সালে জোড়াসাঁকো থেকে চিরবিদায় নিয়ে রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ের উপরে ‘শান্তিধাম’ বানিয়ে চলে যান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ এই শান্তিধামেই তাঁর মৃত্যু হয়। শেষ বয়সে তাঁর সঙ্গী ছিল এক অন্তহীন নিঃসঙ্গতা।
সুদেষ্ণা বসু
সংগৃহিত: আলমগীর হক স্বপন





