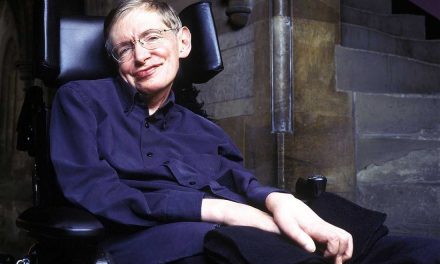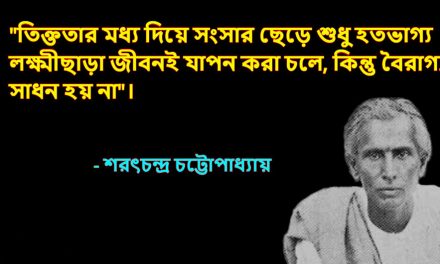বাইশ বছর সাত মাস বয়সের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ফুলশয্যার রাতে তাঁর নয় বছর নয় মাসের বউ ভবতারিণীকে বললেন, আজ থেকে তোমার নাম হলো মৃণালিনী! তখন ভবতারিণীর বুকটা মুচড়ে উঠেছিলো…, আহারে, বাবা-মা কত আদর করে তাঁকে ডাকেন, “ভব—মা, আমার লক্ষী সোনা-মা!” সেই প্রিয় নামটি তাহলে চিরতরে হারিয়ে যাবে!
রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি ‘মৃণালিনী’ শব্দের অর্থ জানো?” ভবতারিণী নীরবে মাথা দোলালেন, জানেন না। তিনি বললেন, “‘মৃণালিনী’ শব্দের অর্থ পদ্ম, পদ্মের সাথে রবির সম্পর্ক আছে। ‘রবি’ শব্দের অর্থ জানো তো? ‘সূর্য’। ভোরের সূর্যের আলো পদ্মের উপর পড়লে তা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। রবি ছাড়া মৃণালিনী যেমন অপ্রস্ফুটিত থাকে, তেমনি মৃণালিনীবিহীন রবিও অপূর্ণ!” এই কথা বলে কবি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।
ভব’র না মেনে উপায় নাই, স্বামী কত বড় মাপের একজন কবি, তার কত নাম- ডাক! স্বামী হিসাবে ভালোবেসে যদি তিনি তাঁর স্ত্রীর নামটা বদলে দেন, ঐটুকু মেয়ে ভব কিভাবে তা বারণ করবে? ঠাকুর পরিবারের বউ হবার পরে, তাঁর ‘ভবতারিণী’ নামটি মুছে গিয়ে ‘মৃণালিনী’ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন সবার কাছে। ভবতারিণী নামটি হারিয়ে গেলো মৃণালিনী নামের আড়ালে।
তবে কবি কোনদিন তাঁকে মৃণালিনী নামে সম্বোধন করতেন না, বা সেই নামে সম্বোধন করে চিঠিও লিখতেন না। ‘ভাই ছোট বউ; ‘ভাই ছোট গিন্নি; ‘ভাই ছুটি’, এইসব সম্বোধন করেই কবি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীকে চিঠি লিখতে উৎসাহ দিতেন এবং তাঁর চিঠির জন্য অপেক্ষা করতেন। কিন্তু মৃণালিনী খুব কম লিখতেন। মৃণালিনীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি পাওয়া গেছে ছত্রিশটি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা মৃণালিনীর দুটো চিঠির বেশি পাওয়া যায় নি।
অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “বিয়ের ব্যাপারে একরকম চাপে পড়েই রবীন্দ্রনাথ নিমরাজি হয়েছিলেন”। অনেক পাত্রী খুঁজে বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির এস্টেটের এক কর্মচারী বেণীমাধব রায়ের বড় মেয়ে ভবতারিণীকেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী হিসেবে বেছে নেয়া হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছায়, খুলনা জেলার দক্ষিণডিহির ফুলতলা গ্রামের ভবতারিণী রবীন্দ্রনাথকে বিয়ে করতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসেন।

রবীন্দ্রনাথে সাথে ভবতারিণী (মৃণালিনী) © Wikipedia
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ের ব্যাপারে গুরুজনদের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়েছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী বেনারসী ‘দৌড়দার’ জমকালো শাল গায়ে দিয়ে তিনি বিয়ে করতে গেলেন। নিজেদের বাড়ির পশ্চিম বারান্দা ঘুরে, বিয়ে করে আনলেন অজ্ঞ বালিকা ভবতারিণীকে। খুবই ঘরোয়া আর অনাড়ম্বরভাবে তাঁদের বিয়েটা ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন হলো। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, “আমার বিয়ের কোন গল্প নাই, আমার বিয়েটা যা তা করে হয়েছিলো”।
কবির বাসরঘরের বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের ছেলের স্ত্রী প্রত্যক্ষদর্শী হেমলতার লেখায়, “বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি শুরু করেন। … ভাঁড় খেলার বদলে তিনি ভাঁড়গুলি উপুড় করে দেন, ছোট কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠেন, ‘ওকি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড়গুলি উল্টে পাল্টে দিচ্ছিস কেন?’ ‘সব যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে–কাজেই ভাঁড়গুলো উল্টে দিচ্ছি’ বলেছিলেন তিনি। তারপরে গান ধরেছিলেন, ‘আ মরি লাবণ্যময়ী…’ আর লজ্জায় ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা নীঁচু করে বসে ছিলেন ভবতারিণী”।
শাশুড়ি যতদিন বেঁচে ছিলেন, বিয়ের আসর থেকেই তিনি সেই বালিকা বধূদের নিজের তত্ত্বাবধনে নিয়ে রাখতেন, তাঁরা কিছুটা বড় হলে আবার নতুন করে ফুলশয্যার আয়োজন করতেন। কিন্তু মৃণালিনী এই বাড়ির বউ হয়ে আসার এগারো বছর আগেই তাঁর শাশুড়ি মারা যান, ফুলশয্যার রাতে জ্ঞানদানন্দিনী সেই নিয়মের অজুহাত দেখালে, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছা হার মানলো, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাতে সেই রাতেই তাদের ফুলশয্যা হলো।
গ্রামের পাঠশালায় প্রথম বর্গ শেষ করা ভবতারিণী ঠাকুরবাড়িতে এসে দিশেহারা অবস্থায় পড়লেন, বিশাল বাড়ি, অনেক লোকজন, আর ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সবাই কি সুন্দর! ছেলের বিয়ে দিয়েই অপরিণত পুত্রবধূকে ঘরসংসার সামলানোর কাজে ব্যস্ত করে তোলেন নি মহর্ষি। তিনি খুবই স্নেহ করতেন তাঁর ছোট পুত্রবধূটিকে। বিয়ের পর প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের দাদা হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী নীপময়ী দেবী মৃণালিনীর শিক্ষার ভার নিলেন। মৃণালিনীকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে মহর্ষি তাঁকে ভর্তি করলেন কলকাতার লরেটো হাউসে। কিনে দিলেন স্লেট, বইপত্র। তৈরি হল মৃণালিনীর স্কুলে যাবার পোশাক। এই সবই ঠাকুরবাড়ির হিসেবের খাতায় লেখা আছে।

মৃণালিনী দেবী সন্তানদের সাথে © Wikipedia
একবছর লোরেটোতে পড়াশোনা করেন মৃণালিনী। পরে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেতে বাড়িতেই পণ্ডিত হেরম্বচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে তাঁর সংস্কৃত শেখার ব্যবস্থা করা হয়।
মেজবৌদি জ্ঞানদানন্দিনী একদিন হাসতে হাসতে তাকে বলেছিলেন, “তুই তো আমার তুলনায় অনেক বড় বয়সে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিস। আমি যখন এখানে আসি, আমার বয়স ছিলো সাত বছর, দুধদাঁত পড়েছে এই ঠাকুর বাড়িতে!”
রবীন্দ্রনাথের বিয়ের রাতে তার জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গাপাধ্যায় জমিদারীর কাজে শিলাইদহে গিয়ে মারা যান, খবরটা তাঁরা পরের দিন জানতে পারেন। শোকের কারণে বিয়ের সব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়, কিন্তু এর ফলে নববধূর কপালে ‘অপয়া’ টিকা লাগে নি। সেই ১৮৮৩ সালে ঠাকুর পরিবার ছিলো সম্পূর্ণভাবে কুসংস্কারমুক্ত।
তারপর কেটে গেছে অনেকটা সময়, অথচ আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এখনও যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে, তবে অবধারিতভাবে সেটা নতুন বউয়ের মাথার উপর দিয়ে যায়। তার কারণেই যে এমন অঘটনটা ঘটেছে, তাতে কারো কোন সন্দেহ থাকে না! ফলাফল, আজীবন তাকে ‘অপয়া’ নামে চিহ্নিত করা হয়! হায়রে কুসংস্কার!!
তাদের বিয়ের এক মাস পরে জ্ঞানদানন্দিনী ভবতারিণীকে মৃণালিনী হিসাবে গড়েপিঠে নিতে তাঁর ২৩৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোড়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘষে মেজে চৌকস করে তোলার দায়িত্ব নিলেন। তাঁকে রবির উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। কিভাবে চুল বাঁধতে হয়, কিভাবে শাড়ি-ব্লাউজ পরতে হয়, শেখাতে লাগলেন। জ্ঞানদানন্দিনীই ঠাকুরবাড়িতে শাড়ি পরার ঢং আর ব্লাউজের পরিবর্তন আনেন। তিনি ভবতারিণীর গেঁয়ো খোলস ছাড়িয়ে বাংলা উচ্চারণ, ইংলিশ চর্চা চালাতে থাকেন।
কালে কালে মৃণালিনী হয়ে উঠেন ব্যক্তিত্বময়ী, সুদর্শনা এক নারী! নানা বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর গায়ের রং ছিল একটু চাপা। আড়ম্বরহীন থাকতেন বলেই সম্ভবত মৃণালিনীর চটক ছিল কম। তিনি সবাইকে সাজাতে পছন্দ করতেন কিন্তু নিজে সাজতেন না। একদিন সবার অনুরোধে কানে দুটি দুল ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ কবি সেখানে উপস্থিত হলে তিনি কানে হাত চাপা দিয়ে দুল দুটি লুকিয়ে ফেলেন।
ঠাকুরবাড়িতে বউদের শিক্ষা শুরু হতো পান সাজা দিয়ে। তারপর তাঁরা শিখতেন বড়ি, কাসুন্দি- আচার করা। মৃণালিনী এইসব কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি নানারকম মিষ্টি তৈরি করতে পারতেন। তাঁর তৈরি দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই, চিড়ার পুলি ছিলো বিখ্যাত! স্ত্রীর রন্ধননৈপুণ্যে কবিও উৎসাহী হয়ে নানারকম রান্নার ‘এক্সপেরিমেন্ট’ করতেন, মানকচুর জিলাপি তারমধ্যে অন্যতম। মৃণালিনীর হাতের গুণে সেটাও ভালোভাবে উৎরে যেতো। মৃণালিনী ভালোবেসে রান্না করতেন আর ভালোবাসতেন পাঁচজনকে ভালোমন্দ রেঁধে খাওয়াতে। সুগৃহিণী বলতে যা বোঝায়, তিনি ঠিক তেমনটাই ছিলেন।
ঠাকুরবাড়িতে সব মেয়ে-বৌয়েরা রাঁধতে পারতেন, তবে তার মধ্যে বেশি নম্বর পেয়েছিলেন মৃণালিনী দেবী আর কাদম্বরী দেবী। শ্বশুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও এই ব্যাপারে কম উৎসাহ ছিলো না! ঠাকুর বাড়িতে অনেক রকমের ব্যঞ্জন হতো— সুক্তানি, পালংশাকের ঘন্ট, আলু-পটলের ডালনা, শিমের কালিয়া, ফুলকপি বিট ও শিমের চচ্চড়ি, লাউপাতা ভাজা, বেগুনপোস্ত, মোচার পাতুরি, কাঁচকলার দম, আলুপোহা, কপি-কড়াইশুঁটির রসা, দই-বেগুন। ডালের মধ্যে — ভাজা মুগডাল, নারকেল দিয়ে মসুর ডাল, কলাই ডাল, মটর ডাল। পাঞ্জাবী কলাইয়ের ডাল ঠাকুরবাড়ির প্রিয় খাবার ছিলো।
মাছও কম রান্না হতো না— কই মাছের পাতুরি, নারকেল চিংড়ি, মাছের ঝুরো, সর্ষে ইলিশ, মৌরালা মাছের অম্বল, আম-শোল, মাগুর মাছের হিংগী, রুই অথবা ভেটকী মাছের মইলু আর মৌরালা মাছের চচ্চড়ি। মৌরালা মাছের চচ্চড়ি তিনি কাদম্বরী দেবীর কাছ থেকে শিখেছিলেন, এই পদটি তার স্বামী রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিলো। তবে তরকারিতে মিষ্টি দেয়ার প্রচলন শুরু হয় ঠাকুরবাড়ি থেকে। মহর্ষি নিজেও মিষ্টি দেয়া তরকারি খেতে খুব ভালোবাসতেন।
খাবার পরিবেশন করাটাও ছিলো দেখার মতো! কাঁসার থালায় ভাত দেয়া হতো, আর থালার চারপাশে সাজানো হতো নানারকম ব্যঞ্জনের পনেরো বিশটি বাটি। জোড়াসনে বসে কবি সেই খাবার খেতেন। সবগুলি ব্যঞ্জন হয়তো খাওয়াও হতো না, তবে খাবার এভাবেই পরিবেশন করা হতো।
মৃণালিনী যখন শান্তিনিকেতন গৃহে যান, তখন দোতলার বারান্দায় একটা উনুন পেতে নিয়েছিলেন। ছুটির দিনে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। শান্তিনিকেতনে মায়ের রান্না করা নিয়ে মীরাদেবী লিখেছেন, “সরু এক-ফালি বারান্দায় একটা তোলা উনুনে মোড়ায় বসে মা রান্না করছেন, তাঁর পিঠটা শুধু দেখা যাচ্ছে”। রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন ভোজন রসিক, মৃণালিনী তেমনই ছিলেন রান্নায় পটু।
বিয়ের পর তিনি কাদম্বরী দেবীর অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখলেন। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে তাঁর স্বামী ও নতুন বৌঠানকে জড়িয়ে অনেককিছুই তাঁর কানে এসেছিলো, তিনি নীরবেই সেসব সামলে নিয়েছিলেন। সামলে নিয়েছিলেন স্বামীর প্রিয় বৌঠানের অপমৃত্যুর গভীর শোক।
জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কবির প্রত্যাশাগুলি পূর্ণ করেছিলেন। কবি যখন শান্তিনিকেতনে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি একটার পর একটা তার গায়ের গয়না খুলে দিয়েছিলেন যাতে করে সেখানকার বাচ্চাদের শিক্ষা ও খাবারের কোন অসুবিধা না হয়। তাঁর এইরকম কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় আত্মীয়স্বজনের উপদেশ, উপহাস, বিরুদ্ধতা, বিদ্রূপ সবই সহ্য করেছিলেন তিনি। কবির হাতে তুলে দিয়েছেন অজস্র গয়না। বিয়ের যৌতুকের গয়না ছাড়াও শাশুড়ির আমলের ভারী ভারী অনেক গয়না ছিলো তাঁর। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “শেষে হাতে কয়েক গাছা চুড়ি ও গলার একটি চেন ছাড়া তাঁর আর কোন গয়নাই অবশিষ্ট ছিলোনা”।
ছোট মেয়ে মীরা স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “শান্তিনিকেতনের দোতলার গাড়িবারান্দার ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মার হাতে একটা ইংরেজি নভেল। তার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিদিমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন”।

মৃণালিনী দেবী স্বামী ও বাচ্চার সাথে © Wikipedia
রামায়ণের সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন তিনি, তবে শেষ করতে পারেননি। রথীন্দ্রের কাছে যে খাতাটি ছিলো, তাতে মহাভারতের শ্লোক, মনুসংহিতা ও উপনিষদের শ্লোকের অনুবাদ করেছিলেন। কবির নির্দেশে তিনি বাংলার রূপকথা সংগ্রহের কাজেও হাত দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সংগ্রহ থেকেই পেয়েছিলেন ‘ক্ষীরের পুতুল’ গল্পটি। মৃণালিনী ঠিক যেমন করে বলেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠিক সেভাবেই গল্পটি লিখেছিলেন। রূপকথার যাদুকরের সেদিন হাতেখড়ি হলো মৃণালিনীর কাছে! অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘এই আমার রূপকথার আদিকথা’।
সাহিত্যচর্চা, অনুবাদ চর্চার পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির নাটকেও তিনি অংশ নিতেন। ‘রাজা ও রানী’ নাটকে তিনি নারায়ণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন । সাহিত্যে আগ্রহ থাকলেও চিঠি আর সামান্য কিছু অনুবাদের খসড়া ছাড়া মৃণালিনী প্রায় কিছুই লিখে যান নি। এই ব্যাপারে মৃণালিনী বলতেন, “তাঁর স্বামী বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেইজন্যই তিনি কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করেন না”।
উনিশ বছরের বিবাহিত জীবনে বেশ লম্বা সময় তাঁকে কাটাতে হয়েছে আঁতুড় ঘরে। বিয়ের দু’বছর পর বেলা, পরের বছর রথীন্দ্রনাথ, তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। এরপর একে একে এলো রেনুকা, মীরা, তারপর শমীন্দ্র। একুশ বছর বয়সে পাঁচ পাঁচটি সন্তান, সাথে সংসার দেখাশোনা করা, সবকিছু মিলিয়ে তখন তাঁর দিশেহারা অবস্থা। তবুও তিনি হাল ছাড়েন নি, এরমধ্যেও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত স্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে।
বিয়ের পর তাঁকে বারবার আবাস বদল করতে হয়েছে। কখনও কলকাতার জোড়াসাঁকো, তো কখনও শিলাইদহ, তো কখনও শান্তিনিকেতন। ১৮৯৮ সালের ৩ অগস্ট পাঁচ ছেলেমেয়েকে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে জোড়াসাঁকো থেকে শিলাইদহে বসবাসের জন্য চলে গেলেন মৃণালিনী। গৃহবিদ্যালয় খুলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শেখানোয় যেমন মন দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাদের স্বনির্ভর করে তুলতে ঘরের কাজ শিখিয়েছিলেন মৃণালিনী।
মৃণালিনী আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথের আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা আরও সার্থক হতে পারতো। তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রমের দেখাশোনা করতেন এবং আশ্রমের কচি কচি শিশুদের অপরিসীম মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। বাড়ির বাইরে এসেও শিশুরা মাতৃস্নেহ পেতো।
সেদিন বোলপুরে এক মুন্সেফের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীকে নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে ছিলো খাওয়া-দাওয়ার বিশাল আয়োজন, যাকে বলে এলাহি কান্ড! অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার জন্য তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে মৃণালিনী পা পিছলে পড়ে জ্ঞান হারান। কবি কোনরকমে বোলপুর থেকে তাঁকে শান্তিনিকেতন নিয়ে আসেন।
১৯০২-এর মাঝামাঝি তিনি এতই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে, ১২ সেপ্টেম্বর তাঁকে নিয়ে যেতে হল কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। প্রায় দুই মাস তাঁর নিরলস সেবা করলেন রবীন্দ্রনাথ। অসুখ ধরা না পড়ায় হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা হল। শেষ রক্ষা হল না তাতেও। কবির সমস্ত সেবাযত্ন তুচ্ছ করে শীতের পদ্মটি ম্লান হয়ে এলো, হারিয়ে গেলো কবির প্রিয় পত্র সম্বোধনটি ‘ভাই ছুটি’। কে জানতো এতো তাড়াতাড়ি এই জীবন থেকে, সংসার থেকে তিনি ছুটি নিয়ে চলে যাবেন! কঠোর শারিরীক পরিশ্রমের তীব্র আঘাত সহ্য করতে না পেরে, আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের মাত্র এগারো মাস পরেই মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি জগৎ-সংসার থেকে চিরবিদায় নিয়ে পাড়ি জমালেন অন্য ভূবনে। ১৯০২-এর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ২৩ নভেম্বর রাতে চলে গেলেন কবিপত্নী মৃণালিনী।
স্ত্রীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ প্রতি পদে পদে তার অভাব অনুভব করেছেন। দুঃখ করে বলেছেন, “এমন কেউ নাই যাকে সব বলা যায়”। অনুভব করেছেন, তাঁর আশ্রম বিদ্যালয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে মৃণালিনীর অভাবে। তিনি বলেছেন, “আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না”।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নিজের সন্তানদের মৃত্যু অবশ্য তাঁকে দেখতে হয়নি। তিনি বড় কন্যা বেলা আর মেজ কন্যা রেণুকার বিয়ে দেখে গিয়েছিলেন।
তথ্যঋণঃ
- ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, লেখক— চিত্রাদেব
- আমি মৃনালিনী নই, লেখক— হরিশংকর জলদাস