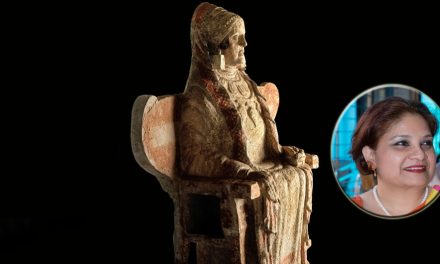বাংলায় ব্রিটিশদের সঙ্গে মুঘলদের প্রথম সম্মুখ সমর হয় আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি, বাংলার নবাব মীর জুমলার নবাবি আমলে। আওরঙ্গজেবের সিংহাসন দখলের প্রধান সেনাপতি মীর জুমলা ১৬৬০দশকে বাংলায় সুবাদার হয়ে আসেন। নতুন সুবাদার যখন গোলকুণ্ডার সুলতানের কর্মচারী সেই সময় থেকে পণ্য আমদানি রপ্তানিতে রাজপথ এবং সমুদ্র নির্ভর বিপুল দেশিয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায় জড়িয়েছিলেন। মুঘল সেনাপত্যের আগের সময়েও ইওরোপিয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল না। জগদীশ নারায়ণ সুরকার ‘লাইফ অব মীরজুমলা’য় দেখিয়েছেন, ইওরোপিয়রা মীর জুমলাকে অস্বীকার করতে পারত না; তার সঙ্গে নিমরাজি হয়েও ব্যবসা করতে বাধ্য হত। একদিকে গুরুত্বপূর্ণ মুঘল রাজপুরুষ এবং অন্যদিকে এশিয়াজোড়া ছড়ানো বিপুল ব্যবসাজালের দরুন ইওরোপিয় সনদি কোম্পানিগুলো তাকে বারবার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।
বাংলা নিয়াবতের অধিকার পাওয়ার সময় থেকেই ব্রিটিশদের সঙ্গে তার বিবাদ শুরু হয়। শুল্ক দেওয়া নিয়ে বিবাদের সূত্রে পাটনা থেকে ব্রিটিশদের যে কটা সোরা ভর্তি নৌকো ঢাকায় আসছিল সব কটাকে তিনি আটক করান। কোম্পানির হুগলী কুঠির মধ্যস্থ ট্রাভিস্টা জামিন হিসেবে মীর জুমলার একটি দেশি নৌকো আটকে করে। ক্ষিপ্ত সুবাদার ব্রিটিশদের সব কটা কুঠি ধ্বংস করে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়া করার হুমকি দেন। কোম্পানি থেকে ট্রাভিস্টাকে নির্দেশ দেয় মীর জুমলার আটক করা নৌকোটি ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে। এজেন্ট ট্রাভিস্টা ক্ষমা চেয়ে নেন। বিবাদ মিটে যায়।
মীর জুমলার সঙ্গে মুখোমুখি বিবাদ বাংলায় ব্রিটিশ কোম্পানির নবযুগের সূচনা করল। এবার থেকে ব্রিটিশেরা ভাবতে শুরু করে কীভাবে তারা স্থানীয় আমলাদের দয়াদাক্ষিণ্য ছাড়াই ব্যবসা বাড়াবে এবং কুঠির সুরক্ষা ঢেলে সাজাবে। তারা মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৬৮৬তে প্রথম মুঘল-ব্রিটিশ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যে কুঠিয়ালেরা ১৬৬১ মুঘল নৌকো দখল করার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তারা ২৫ বছর পর ১৬৮৬ সালে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে ঘোষণা করে মুঘল জাহাজ দখল করে এবং বন্দরেও আগুণ লাগয়ে দেয়।

১৬৬৪তে বাংলার নবাব হিসেবে আসা শায়েস্তা খানের সঙ্গেও ব্রিটিশদের মধুর সম্পর্ক তৈরি হল না। যদিও তিনি ব্রিটিশদের দেওয়া শাহ সুজার নিশানের শর্তাবলী মানতে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু বাস্তবে আমলাদের সেটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। বাংলা আর সুরাটের মধ্যস্থরা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে লন্ডনের কর্তাদের আর্জি জানায় এবং দাবি করে কোম্পানি যেন যে কোনও উপায়ে সুরক্ষা বাড়ানো বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করে।
ভারতে ব্যবসা বাড়াবার জন্যে মুঘলদের বিরুদ্ধে “তীব্র এবং আগ্রাসী” যুদ্ধের প্রথম ডাক দেন ১৬৬৯ কোম্পানির সুরাটের প্রেসিডেন্ট এবং বম্বের গভর্নর গারল্যান্ড অঙ্গিয়ার। ১৬৭৭এ তিনি লন্ডনের কর্তাদের প্রস্তাবটা লিখলেন। প্রথমের দিকে কর্তারা প্রস্তাবটি গুরুত্ব না দিলেও, তার প্রস্তাব গুরুত্ব পেল ১৬৮১তে যশুয়া চাইল্ড গভর্নর হওয়ার পর। যশুয়া ভারতে আরও সক্রিয়তার নীতিতে(ফরোয়ার্ড পলিসি) এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন।
যদিও কোর্ট অব ডিরেক্টর্স মুঘলদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল না(সংক্ষেপে কারণগুলো ছিল ১) খুব খরচসাপেক্ষ, ২) মুঘলের শুধু বাংলা বা সুরাট নয় সারা দেশে কোম্পানির ওপর আঘাত নামিয়ে আনবে, ৩) ডাচেরা মুঘলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আক্রমনে নামতে পারে, ৪) বাংলায় আক্রমন খুব প্রভাবশালী হবে না কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য খুব কম, কিন্তু বম্বেতে আক্রমন করলে ভারত মহাসাগর আর লোহিত সাগরের বন্দর, পারস্য ইত্যাদি অঞ্চলের ২০ থেকে ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের ব্যবসা মার খেয়ে যাবে ইত্যাদি), কিন্তু চিঠিপত্রের সূত্রে আমরা বুঝতে পারি, তারা দুর্গ ইত্যাদি তৈরি করে সুরক্ষা দেওয়ার প্রশ্নে মুঘলদের না চটানোর প্রকাশ্য অবস্থানকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও, কুঠি/বাসস্থান সুরক্ষার বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছিল। কোম্পানি ১৬৮৬র সনদে সম্রাট দ্বিতীয় জেমসের থেকে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সম্মতি আদায় করে।
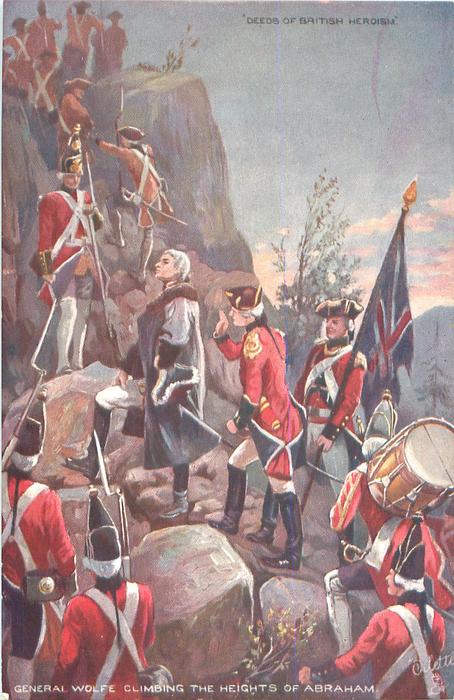
কর্তারা যুদ্ধের বিস্তৃত পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি নেন। তখনও সমুদ্রে যে সব বাহিনী নামে নি, সেগুলিকে তারা মাদ্রাজ থেকে বাংলায় পাঠায়। কোম্পানির যুদ্ধ এডমিরাল হলেন নিকলসন। তাকে রসদ এবং বাহিনী আর কোম্পানির অন্যান্য আমলা নিয়ে বালেশ্বরের দিকে রওনা হতে বলা হল। বহরটিকে বাংলার জন্যে আলাদা ভাবে তৈরি করা হয়েছিল। নিকলসন নবাবকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেও নবাবের দিক থেকে কোন সদর্থক উত্তর পাওয়া গেল না। বাহিনী চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে “শহর, দুর্গ এবং জনপদ” দখল ধ্বংস লুঠ করতে থাকে। বহরে ছিল ছটা জাহাজ। কিন্তু ১৬৮৬র অক্টোবরে হুগলীতে লড়াই শুরু হলে মাত্র তিনটে জাহাজ অকুস্থলে পোঁছল। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকতে না পেরে হুগলীর ২৬ মাইল দূরে সুতানুটিতে বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। দুপক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। ব্রিটিশরা শাহী লবন গুদাম পুড়িয়ে দেয়, থানা দুর্গ তছনছ করে এবং হিজলি দ্বীপ দখল করে। মুঘলেরা ব্রিটিশদের হিজলি থেকে তাড়াতে ব্যর্থ হয়। আবার নতুন করে দরকষাকষি শুরু হয়। ইতোমধ্যে ক্যাপ্টেন হিথের নেতৃত্বে নতুন বাহিনী পাঠানো হয়। আওরঙ্গজেব তখন বিশাল সৈন্য নিয়ে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে ব্যস্ত, তাঁর সাম্রাজ্যের প্রান্ততম প্রদেশ বাংলায় (যেখানে তিনি একবারও পা দেন নি) এইরকম খুচখাচ যুদ্ধ বিষয়ে মন দেওয়ার সময় ছিল না। তাছাড়া সামরিক শক্তি হিসেবে তিনি ব্রিটিশদের পাত্তাই দিতেন না – “যখন শুনে পাদশাহ হুগলীর ঠিকঠাক মানচিত্র তৈরি করে তাকে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন”। শান্তির কথাবার্তা চলার সময়েই হিথ আর চার্ণক বালেশ্বর আক্রমন করে চট্টগ্রাম দখল করতে পৌঁছলে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশরা মুঘলদের বিরুদ্ধে সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরাকান রাজাকে প্রস্তাব দিল। আরাকান রাজ ব্রিটিশ প্ররোচনায় পা দিলেন না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশেরা মাদ্রাজে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ফেব্রু ১৬৮৯তে(যুদ্ধের বিশদ বিবরণ, যুদ্ধের প্রস্তুতি ইত্যাদির বিষয়ে জানতে দেখুন হেজেসেস ডায়েরি, ২ খণ্ড, ৫০-৮৭)। ব্রিটিশদের বাংলা ছাড়া করা হল, বাংলার বাণিজ্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।
এরপরে শান্তিচুক্তি হল। শান্তিচুক্তির হাত ধরে ব্রিটিশ কোম্পানি নতুন করে বাংলায় ফিরে আসে। তাদের ডেকে আনেন বাংলার নতুন সুবাদার “গুড এন্ড ওয়ার্দি নবাব” ইব্রাহিম খান। তিনি জানালেন সম্রাট ব্রিটিশদের অনুশোচনা খোলা মনে গ্রহন করেছেন। আওরঙ্গজেব বাংলার নবাবকে লিখেছেন, ব্রিটিশেরা ‘তাদের হীন দুষ্কর্ম ক্ষমা করার আবেদন করেছে’। তিনি ব্রিটিশদের মাত্র ৩০০০ টাকার বিনিময়ে শুল্কবিহীন বাণিজ্য করতে দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এ বিষয়ে হাসবুলহুকুম বা শাহি নির্দেশ ১৬৯১তে জারি হয় শাহী দেওয়ান আসদ খানের পাঞ্জা এবং স্বাক্ষর সহ। বাংলার কুঠিয়াল আনন্দে লিখল, “আমরা… ঢাকা থেকে… মাত্র ৩০০০ টাকার বাতসরিক পেশকাশের বিনিময়ে সম্রাটের হাসবুলহুকুমের নকলটি পেয়েছি যা অপ্রত্যাশিত আনুকূল্য, এর ফলে এবার থেকে সম্মানিত কোম্পানিকে আর কেউ রুখতে পারবে না এবং কেউ খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না”। এই যুদ্ধের ফলে কোম্পানি এবার থেকে তার প্রধান প্রশাসনিক দপ্তর সুতানুটিতে সরিয়ে আনল, হুগলী ছাড়ায় কলকাতা শহরের পত্তনের ভ্রুণ স্থাপিত হল।