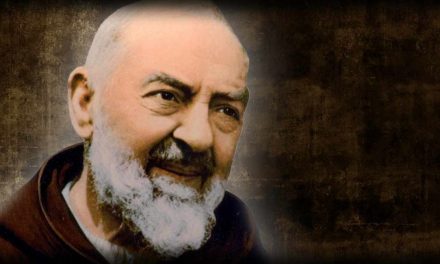ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের শুরুর গল্পটা যেমন জটিল ছিলো, তেমনি জটিল ছিলো এর পতনের গল্পটাও। তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বিশাল বিশাল বৌদ্ধ বিহারগুলো কিন্তু আজও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত বিশাল কোনো বৌদ্ধ বিহারের কথা উঠলেই বর্তমান ভারতের নালন্দা মহাবিহারের কথাই মনে হয়ে থাকে আমাদের, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহার আমাদের বাংলাদেশেই অবস্থিত। বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত এই বৌদ্ধ বিহারের নাম ‘পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার’, যেটি আগে ‘সোমপুর বিহার’ নামে পরিচিত ছিলো।
বিশ্বের বৃহত্তম এই বিহারটি উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট বিস্তৃত চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ওপর অবস্থিত। প্রায় ৭০ ফুট উঁচু চূড়াবিশিষ্ট বিহারটিকে দূর থেকে দেখলে বিশালকায় কোনো পাহাড়ের মতোই মনে হয়। আর এ জন্যই পরবর্তীতে এই জায়গা এবং বিহার উভয়ের নামই দেয়া হয় ‘পাহাড়পুর’।
দীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে ধর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দন্ডায়মান থাকা এই বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন দ্বিতীয় পাল রাজা ধর্মপাল। বহু দূর-দূরান্ত থেকে এখানে আসা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের কাছে এই বৌদ্ধ বিহারটিই ছিলো এক সময়ের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হ্যাঁ, অবাক লাগলেও সত্যি যে, বর্তমানের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এই পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার এক সময় ছিলো ভারতবর্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাপীঠ, যা শুধু ভারতবর্ষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেই আকার প্রদান করে নি, বরং সেই সাথে ভারতবর্ষের রাজনীতিকেও দিয়েছিলো একটি সুস্পষ্ট রূপ।

সোমপুর মহাবিহার, বাংলাদেশ © Wikipedia
নালন্দা মহাবিহারের চাকচিক্য ও প্রচারণার আড়ালে পাহাড়পুরের এই শান-শওকত প্রচ্ছন্ন হয়ে গেলেও ২০১৯ সালে ইতিহাসবিদ সংযুক্তা দত্তের ‘বিল্ডিং ফর দ্য বুদ্ধা’ বইটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোমপুর বা পাহাড়পুর বিহারই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার।
সমগ্র বাংলা অঞ্চকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করবার প্রচেষ্টারই একটি অংশ ছিলো বাংলায় এই মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা। ২০২১ সালে অধ্যাপক রায়োসুক ফুরুই তার ‘আর্লি মেডিয়েভাল বেঙ্গল’ নামের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন, এই ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলটি সে সময় অনেকগুলো ছোট ছোট এককে বিভক্ত ছিলো, যার ‘পুন্ড্রবর্ধন’ নামে পরিচিত উত্তর অংশটি ভারতবর্ষের একটি মহান নগরী ও প্রাদেশিক কেন্দ্র ‘বিহার’ এর সাথে যুক্ত ছিলো এবং বঙ্গীয় ব-দ্বীপ ও বর্তমান মায়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত দক্ষিণাংশটি ছিলো একটি প্লাবিত, কর্দমাক্ত ও ম্যানগ্রোভঘন ভূখণ্ড।
এই উত্তরবঙ্গ, অর্থাৎ পুন্ড্রবর্ধন পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের গভর্নরদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরপরই উর্বর এই অঞ্চলটিতে বহু যুদ্ধবাজদের আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। তখন বাংলায় এক নতুন শক্তির উত্থানের মাধ্যমে এই পর্যায়টির অবসান ঘটেছিলো। আর উত্থিত এই নতুন শক্তিই ছিলো ‘পাল সাম্রাজ্য’।
অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে বৌদ্ধ ধর্ম যখন কাশ্মীরের মতো পুরনো কেন্দ্রগুলোর অধীনস্থ হয়েছিলো, তখন পাল সাম্রাজ্যের রাজারা সফলভাবে বাংলার বন্য অঞ্চল ও সীমান্তের বেশিরভাগ অঞ্চলগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিলো।

সোমপুর মহাবিহার প্রাঙ্গণের দেয়াল © Wikipedia
বিহার সে সময় আগে থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিলো। পালরা গাঙ্গেয় সমভূমির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আনবার জন্য সম্ভবপর সব রকমের চেষ্টা শুরু করলেন এবং বোধগয়া ও নালন্দা মহাবিহারের মতো পবিত্র বৌদ্ধ বিহারগুলোতে মূল্যবান উপহারও দিতে শুরু করলেন, যেনো তাদের শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়। এ ছাড়াও নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলোর সীমানার মধ্যেও সোমপুর, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা করলেন তারা।
সোমপুরে আবিষ্কৃত বেশ কিছু সীলমোহরে রাজা ধর্মপালের শিলালিপি রয়েছে, যেখানে তাকে একজন শ্রদ্ধেয় ভগবানের মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং বৌদ্ধ বিহারের একজন মহান ভিক্ষু হিসেবে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মপাল সে সময় পাল বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং তার এই শক্তি ও প্রতিপত্তিকে প্রকাশ করবার জন্যই সোমপুর বিহারটিকেও ঠিক অনুরূপভাবেই নির্মাণ করা হয়েছিলো। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠা মূলত রাজা ধর্মপালের ক্ষমতার স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলারই একটি অংশ ছিলো।
আগেই বলা হয়েছে, সোমপুর বিহারটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রতিটি দিক অদ্ভূতভাবে প্রতিসম। বিহারের ৭০ ফুট উঁচু ছাদটিও ইচ্ছাকৃতভাবেই বক্রাকৃতিতে তৈরী করা হয়েছিলো, যেনো একে দেখতে শক্তিশালী কোনো পাহাড়ের মতোই মনে হয়। হিন্দু মন্দিরগুলোর মতোই এর নির্মাণশৈলীতে একটি পবিত্র জ্যামিতিক আকারের প্রদর্শন সুস্পষ্ট করা হয়েছে। বিহারের ইটের কাঠামোটি বক্রাকার পাথর খোদাই করে সজ্জিত করা হয়েছে।
শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্য বরাদ্দ ছোট ছোট ঘরবিশিষ্ট বিশাল এই বিহারটির চারদিকে যতো বর্গ কিলোমিটার জুড়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে, ততোটুকুর পরিমাপেই এটি স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আর কোনো বৌদ্ধ বিহার নেই। এমনকি ধারণা করা হয়, প্রাচীরের বাইরেও এই বিহারের সীমানা আরও প্রসারিত এবং ভবিষ্যতে আরও খনন কাজ সংঘটিত হলে এই অজানা সীমানা বেরিয়ে আসবে। সুতরাং পাহাড়পুর বিহারের আকার ও এর প্রদর্শিত প্রতিপত্তি নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটির শিল্পকর্ম © Wikipedia
বৌদ্ধ বিহারগুলো সব সময়ই ধর্মীয় কেন্দ্র হওয়ার পাশাপাশি ছিলো শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞান অর্জন করতেন এবং রচিত শাস্ত্রগুলোর অনুলিপি তৈরী করতেন। আর এই অনুলিপিগুলো করা হতো এখন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ভাষায়, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায়।
ভারতের শিব মন্দিরগুলোর সাথে এই বৌদ্ধ বিহারগুলোর অনেক মিল ছিলো। বিহারে গৌতম বুদ্ধ এবং অন্যান্য ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তিগুলোকে দুধ ও সুগন্ধিযুক্ত পানি অর্পণ করা হতো। সুগন্ধি ধূপ পোড়ানো হতো এবং ভালো মানের কাপড়েরও ব্যবহার হতো।
রোনাল্ড এম. ডেভিডসন ২০০২ সালে ‘ইন্ডিয়ান এসোটেরিক বুদ্ধিজম’-এ লিখেছেন, মধ্যযুগের সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজা-বাদশাহদের মতোই আচরণ করতেন। তারা মহাবিহারের অধীনে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য ছোট ছোট বিহার স্থাপন করতেন। এমনকি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং বিহারের সম্পদগুলো, যেমন, জমি, সোনা, বই-পুস্তক, প্রত্নবস্তু প্রভৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীও তারা গড়ে তুলতেন। সোমপুর বিহারের অদ্ভূত প্রতিসম চারকোণা কাঠামোটিও যেনো বার বার এটিই নির্দেশ করে যে, বিহারটি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের অভ্যন্তরেও একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলো।

দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটির শিল্পকর্ম © Wikipedia
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার-আচরণ ও কার্যাবলি অর্ধ-ঐশ্বরিক ধরনের ছিলো এবং তারা সমাজ ও রাজনীতির সাথে সব সময়ই এক ধরনের প্রশ্নবিদ্ধ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তবে শুরুর দিকে বিহারগুলোতে যখন পাল সাম্রাজ্যের অনুদান আসতো, তখন এই বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও পাল সাম্রাজ্যের সাথে একত্র হয়ে কাজ করতেন।
প্রফেসর ফুরুই ২০২০ সালে ‘ল্যান্ড অ্যান্ড সোসাইটি ইন আর্লি সাউথ এশিয়া’-তে লিখেছেন, প্রথম দিকে পাল সাম্রাজ্যের সামন্তরা সোমপুর মহাবিহারে দান করতেন ভিক্ষুদেরকে এর প্রতিষ্ঠাতা সম্রাটের প্রতি একাত্মতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই, তবে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই উদ্দেশ্যটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভদ্রনাগ নামের একজন সামন্ত রাজা সোমপুর মহাবিহারে একটি সুগন্ধি উপাসনা কক্ষ স্থাপন করেন এবং তার অধিকৃত সম্পূর্ণ একটি গ্রামকেই তিনি এটিকে সমর্থন করার জন্য দিয়ে দেন। ভদ্রনাগ নিজে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা না হলেও পাল সাম্রাজ্যে তিনি বিস্তৃত জমির মালিক ছিলেন। তার এমন কর্মকান্ডের মাধ্যমে মহাবিহার সম্পূর্ণরূপে করমুক্ত হয়ে যায়, যা সরাসরি সাম্রাজ্যের ওপর তার দখল আরোপের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ছিলো। সামন্তদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড পাল সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের ভিত্তিকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দেয় এবং একটা সময় তা গাঙ্গেয় সমভূমিতে যুদ্ধের সূচনা করে।

বিহারের একাংশ © Wikipedia
নবম শতাব্দী থেকে পাল রাজারা উত্তরবঙ্গের বিহারগুলোতে অনুদান প্রদান করা বন্ধ করে দেন এবং রাজকীয় সেবা ও সমর্থন পাবার আশায় তারা ব্রাহ্মণদেরকে অনুদান দিতে শুরু করেন। তবে অন্য দিকে রাজ্য তার জমির মালিকানায় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চাইলে সামন্তদের কাছ থেকে ভূমির অনুদান পাবার আশাও বন্ধ হয়ে যায়। এক দিকে উত্তরবঙ্গে পাল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিলো, আর অন্য দিকে দক্ষিণবঙ্গ একটি কৃষি রাজ্য ও নতুন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করেছিলো।
২০১৫ সালে ইতিহাসবিদ মোনালিসা লাহা ‘সাম সিলেক্টেড বুদ্ধিস্ট মোনাস্টারিজ অ্যাজ সেন্টারস ফর লার্নিং অফ দ্য পালা পিরিয়ড’-এ লিখেছেন, এগারো শতকের দিকে যখন সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে অসংখ্য শিলালিপি, মুদ্রা, সীলমোহর এবং ব্রোঞ্জ ও পাথরে খোদাই করা ছবিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিলো; তখন এই সমৃদ্ধ সম্পদের ভান্ডার দেখে বিহারের সন্ন্যাসীরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন।
পাল সাম্রাজ্যের নিয়তিই যেনো এই সোমপুর বিহারের সাথে আবদ্ধ ছিলো, একেবারে শুরু থেকে শেষ অবধি। সোমপুর বিহার যেমন করে আস্তে আস্তে ক্ষয়ে পড়ছিলো, ঠিক তেমনি এগারো শতক থেকে পাল সাম্রাজ্যেও একের পর এক সামরিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছিলো। ১০২২ থেকে ১০২৩ সালের দিকে চোল সম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র পাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপর কালাচুরি রাজবংশের অত্যাচারী রাজা লক্ষ্মীকর্ণ দক্ষিণবঙ্গকে কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে ‘ভাঙ্গালা’-য় নিজস্ব রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হন। তার বংশের অন্যান্য রাজাদের মতোই তিনিও শৈব মতাদর্শে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদের সাথে একতাবদ্ধ হন। এরই পরিণতিস্বরূপ বোধিবৃক্ষের ছায়ায় গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের প্রায় দেড় হাজার বছর পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের সূর্য স্তিমিত হতে শুরু করে।
২০১২ সালে ইতিহাসবিদ বেদাশ্রুতি ভট্টাচার্যের ‘ভার্মানস ইনকার্সন অ্যান্ড স্যাকিং অ্যান্ড বার্নিং অফ সোমপুরা মাহাবিহারা’-তে একটি দুঃখজনক ঘটনার শিলালিপির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। করুণাশ্রীমিত্র নামের একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, যিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন, বিহার ত্যাগে রাজি না হওয়ায় তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় ভাঙ্গালার সেনাবাহিনী এবং তিনিও সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান।

আকাশ থেকে তোলা দৃশ্য © Wikipedia
শেষ পর্যায়ে পাল সাম্রাজ্যের কারোরই সোমপুর বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ছিলো না। এক সময় যারা সোমপুর বিহারে অনুদান দিতেন, তারাই নিজস্ব মালিকানাধীন মহাবিহার তৈরীতে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এক শতাব্দী পর যখন দিল্লি সালতানাত ও এর উত্তরসূরিদের শক্তি উন্মোচিত হয়, ততো দিনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহারটি ইটের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়তে শুরু করেছে, যেখানে হয়তো আজও বিস্মৃত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।
রেফারেন্স: