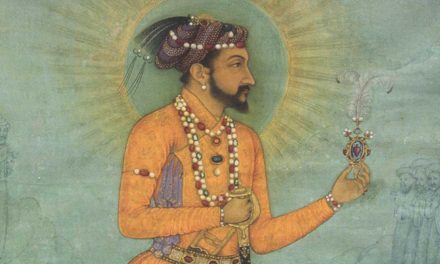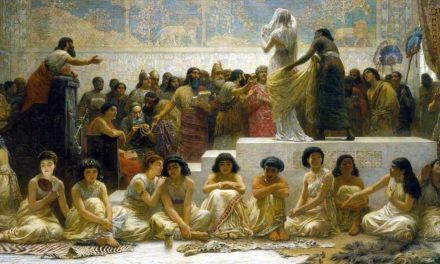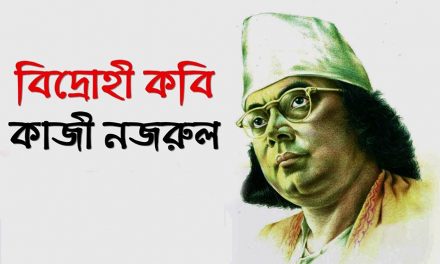অনেকক্ষণ যাবৎ আশেপাশে কোনো জীবিত মানুষকে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ভেসে আসছে করুণ আর্তনাদ, যা বাতাসে ভাসতে ভাসতে কানে এসে বিঁধছে। এই সুর স্বাভাবিক নয়—স্বাভাবিক হওয়ার কথাও নয়। আমি এখন ধুলো-বালিতে আচ্ছন্ন এক জায়গায় শুয়ে আছি; কিছুক্ষণ আগেও এটি ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। চারদিকে ঘরবাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে, ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে গেছে, দিনের কোন প্রহর চলছে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো ভাবছেন—এমন তাণ্ডবের জন্য দায়ী কে? ঐ তো! দেখতে পাচ্ছি তাকে—রুক্ষ চেহারার সেই দানব আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে বুক চিরে তার প্রাণ বের করে আনি… কিন্তু পারবো না। কারণ আমি মৃত—কলিঙ্গের এক সৈন্য। আমার পরিবার, সন্তানদের আর কখনো দেখা হবে না, অথচ প্রাণহীন চোখে দেখতে হচ্ছে সেই ঘৃণাত্মক চেহারা। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি—সম্রাটের চোখে জল। পাষাণ হৃদয়ে কি সত্যিই অনুতাপের স্রোত আছে? তিনি পরম মমতায় আমার চোখ দুটি বন্ধ করে দিলেন—এক পতিত সৈন্যের প্রতি এমন আচরণ কি সম্ভব? হয়তো এই মুহূর্তটাই তার জীবনের মোড় ঘোরানোর শুরু।

অমরাবতী হতে প্রাপ্ত সম্রাট অশোকের সম্ভাব্য মূর্তি
সময়টা তারপর সরে আসে ১৭৮৯ সালে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনস বহু পরিশ্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ও গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে নিজের গবেষণা লিখে শেষ করেছেন; সেটি Asiatic Researches পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে সাড়া মিলতে থাকে। যদিও হিন্দু শাস্ত্রে বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলা হয়, বহু ব্রাহ্মণ তখনও বুদ্ধকে ধর্মদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবেই দেখতেন। ইউরোপে ‘বুদ্ধ’ নামটি জনপ্রিয় হয় মূলত মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তের মাধ্যমে। জোনসের উদ্যোগে পালি ও সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থের খোঁজ একের পর এক মিলতে থাকে, এবং তিনি নিশ্চিত হন—বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষের মগধে; প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ, যিনি ‘শাক্যমুনি’ নামেও পরিচিত। জন্ম-মৃত্যু উভয়ই মগধেই—এ ধারণা তখন ক্রমে পোক্ত হতে থাকে।
কিন্তু জোনসের আসল কৌতূহল ছিল রহস্যময় স্তম্ভগুলো নিয়ে—যেগুলোর কায়া দীপ্ত, শিলালিপি অস্পষ্ট। চতুর্দশ শতকে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দুইটি অসাধারণ স্তম্ভ উদ্ধার করে রাজধানীতে তুলে আনেন; একটি সোনালি আভায় চকচকে বলে ‘মিনার-ই-জরিন’ নামও চলে আসে লোকমুখে। ধীরে ধীরে দেখা যায়—এই ধরনের মনোমুগ্ধকর স্তম্ভ ভারতবর্ষজুড়ে ছড়িয়ে আছে। ইউরোপীয় অনেকেই ধরে নেন, এমন কাজ হয়তো গ্রীকরাই করেছে; ভারতীয়দের পক্ষে এমন নির্মাণ কল্পনা করাও নাকি কঠিন! জোনস ঠিক এটিই ভাঙতে চেয়েছিলেন—স্তম্ভের ভাষা-বয়ান উদ্ধার করে প্রাচীন ভারতের নিজস্ব ইতিহাস তুলে ধরতে। কিন্তু ১৭৯৫ সালে তার আকস্মিক মৃত্যু সেই রহস্য উন্মোচনের কাজকে স্তিমিত করে দেয়।

কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রতীকী ছবি © Roar বাংলা
জোনসের মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদনা-ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ঢিলেমি চলে এলেও, অন্যদিকে ভারতের প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল কলিন ম্যাকেঞ্জি নিজ চেষ্টায় নথি-নকশা সংগ্রহে মন দেন। পরে স্কটল্যান্ডের ফ্রান্সিস বুকানন (বুকানন-হ্যামিল্টন নামেও পরিচিত) সরকারিভাবে ব্রহ্মদেশ, নেপাল, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও শেষে বাংলা-বিহার অঞ্চলে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেন; বৌদ্ধ ধর্মের মূল শেকড়ে পৌঁছানোর সূত্র পাওয়া যায় এখান থেকেই। এসব প্রচেষ্টাই পরবর্তীকালের বড় উন্মোচনের পটভূমি প্রস্তুত করে।

অশোকের স্তম্ভ © wikipedia
১৮৩২ সালে তরুণ জেমস প্রিন্সেপ প্রায় মৃতপ্রায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। তিনি উইলিয়াম জোনসের অসমাপ্ত কাজ হাতে নিয়ে শিলালিপির অক্ষরমালা ভাঙতে বসেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মী লিপি পাঠোদ্ধার করেন; খরোষ্ঠীরও সূত্র মিলতে থাকে। এর পর্দা সরাতেই উন্মোচিত হয় ‘দেবনামপিয়তিস্য’ বা ‘প্রিয়দর্শী’ নামে স্বাক্ষরকারী সম্রাটের পরিচয়—তিনি আর কেউ নন, মৌর্য সম্রাট অশোক, অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রিয় পৌত্র। ১৮৩৮ সালের মধ্যে প্রিন্সেপ স্তম্ভ ও শিলালিপির অধিকাংশ পাঠ অনুবাদ করেন এবং প্রমাণ করেন—অশোকই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক; তার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারত ছাড়িয়ে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান, মিয়ানমার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।
প্রচলিত মতে গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ সালে, আর জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের মৃত্যুবছর খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৮। জৈন ধর্মের বিস্তার তুলনায় আগেই থমকে গেলেও বৌদ্ধ ধর্ম দীর্ঘকাল ছড়িয়ে থাকে—এর কৃতিত্ব অশোকের নৈতিক–অহিংস নীতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় বার্তা ও মিশনারি তৎপরতার। কলিঙ্গ যুদ্ধ (প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৬১)–পরবর্তী অনুতাপই ছিল তার রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দু; শিলালিপির বয়ানে নিহত-বন্দির বিপুল সংখ্যা, নির্বাসন—সব মিলিয়ে এক বিভীষিকাময় চিত্র উঠে আসে। সেই ভয়াবহতার পর অশোক তলোয়ার নামিয়ে ‘ধর্ম’কে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে সামনে আনেন, সহনশীলতা ও করুণার ভাষাকে স্তম্ভলিপিতে খোদাই করতে থাকেন। জৈন ধর্ম সম্পর্কে কিছু পরবর্তী বর্ণনা অশোকের বিরাগের কথা বললেও ইতিহাসবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে; অশোকের নিজস্ব শিলালিপিগুলোতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতার কথাই প্রধানভাবে উচ্চারিত।
এখন হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন জাগছে—লেখার শুরুতে যে বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াল দৃশ্য, তার জন্য দায়ী কে? ইতিহাস বলছে, সেই রক্তাক্ত কলিঙ্গ যুদ্ধের নেপথ্যের নেতৃত্বে ছিলেন সম্রাট অশোক নিজেই—যার চোখের জল পরে কোটি মানুষের ধর্মপথে আলোর দিশা হয়ে ওঠে। আর এই সম্রাটকে বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে তারও আগে—খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, যখন ভারতবর্ষে ছিল ষোলটি মহাজনপদ, এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মগধ… .<চলবে>