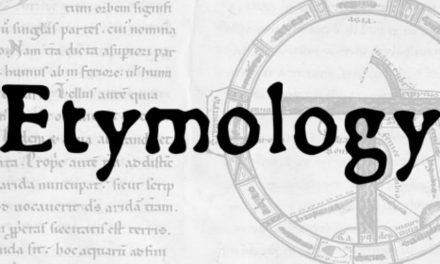বাংলা সাহিত্যে মুজতবা আলীর পরিচিতি রম্যলেখক হিসেবে। একজন বিংশ শতাব্দীর বাঙালি সাহিত্যিক। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, অনুবাদক ও রম্যরচয়িতা। তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনির জন্য বিশেষভাবে জনপ্রিয়। বহুভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য এবং রম্যবোধে পরিপুষ্ট। তাঁর লেখনিতে হাস্যরসগুলি ছিল বাস্তবের সাথে সম্পর্কিত। জীবনের ভেতর থেকে গভীরতমভাবে জীবনকে দেখার তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি ছিল বলেই হাস্যরসের মধ্যে পরিমিতভাব ছিলো। যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে, ততোদিন তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যদিয়ে পাঠকদের কাছে বেঁচে থাকবেন। তাঁকে একবার এক জার্মান পণ্ডিত জিজ্ঞেস করেছিলেন, শেক্সপীয়রের কোন লেখাটা আপনার ভালো লাগে? ঝটিকা উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যামলেট! তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, ঐ একটা বই-ই পড়েছি কিনা!
সৈয়দ মুজতবা আলী এক জায়গায় লিখেছিলেন- তিনি চাকরি পেলে লেখেন না! চাকরি না থাকলে লেখেন।চাকরি তিনি বারবার কেন খুইয়েছেন, এই নিয়ে একটা গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দরখাস্ত নামে একটা রচনায় তিনি লিখেছেন, একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে লেখা ছিল- তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কী? উত্তরে লিখেছিলুম- কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া! তা হলে চলে কী করে? তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছ সাহেব, আমি চাকরিগুলো দেখছি! এটা সত্যি ঘটনা!
একবার মুজতবা আলী লিখলেন, “পেটের দায়ে লিখছি মশাই, পেটের দায়ে! … খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। যেটুকু হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক্ লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কিনা, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোল্ড ব্লাডেড, যে রকম কোল্ড ব্লাডেড খুন হয়- অর্থাৎ আত্মীয়- স্বজনঠিক করে দিয়েছিলেন কিনা? -শবনমের সঙ্গে আবার দেখা হলো কিনা, “চাচা”টি কে, আমি আমার বৌকে ডরাই কিনা- ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাঘ সিঙ্গি নন্দলাল, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মতো খাটাশটাকেও এক নজর দেখে নিতে চান! কারণ কোলকাতার ফেরার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতোমধ্যে আর কি করা যায় এবং এসে রীতিমত হতাশ হন…!”
এক সময় ঠাট্টা করে বলা হতো, যে লেখা পড়লে কিছুই মানে বোঝা যায় না, তারই নাম আধুনিক কবিতা। সেই রকমই এক সময় এমনই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, যখন, যে লেখা পড়তেই ইচ্ছে করে না, তারই নাম ছিল প্রবন্ধ। সৈয়দ মুজতবা আলীই প্রবন্ধকে সেই অকাল মৃত্যুদশা থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি অন্তত একশোটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে, সাতটি ভাষা সেঁচে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা-ই বিতরণ করেছেন তাঁর রচনায়। এগুলো প্রবন্ধ ছাড়া আর কি? এক সময়ে কুকুর পুষেছিলেন। অ্যালসেশিয়ান। পোষ্যটিকে ‘মাস্টার’ বলে ডাকতেন। কেন? কারণ তার প্রভু তিন গেলাসের বেশি খেতে আরম্ভ করলেই মাস্টার ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতে শুরু করত। মানে প্রভুর উপরে মাস্টারি করত। মুজতবা আলী বলতেন, ‘গত জন্মে এ ব্যাটা নিশ্চয় আমার চাচা ছিল।’ তাঁর যে প্রতিভা ছিলো তার সিকিভাগও তিনি লিখে রেখে যেতে পারেননি। ভয়ংকর অলসতার কারণে তিনি নিজেই নিজেকে ঠকিয়েছেন। সুনীতি বাবু বলেছেন, “মুজতবা আলী তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের প্রচ- গবেষক হতে পারতেন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সার্থক অন্বেষণ চালাতে পারতেন, ভারতীয় ইতিহাসের অনুদ্ঘাটিত দিক উন্মোচন করতে পারতেন, কিন্তু কিছুই করেন নি। শুধু ব্যঙ্গ রসিকতায় নির্বাসন দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করলেন।” ভীষণ অগোছালো ছিলেন তিনি।তিনি নিজেই লিখেছেন ‘হাঁড়িতে ভাত থাকলে সাঁওতাল কাজে যায় না, আর আমার ড্রয়ারে টাকা থাকলে আমি লিখি না।’ তারপরেও বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর উপমা একমাত্র তিনিই।
তাঁর রসগোল্লা রম্যগল্পের কাহিনীটা বলি—- গল্পের ঝান্ডুদা বন্ধুর মেয়ের জন্য এক ভ্যাকুম প্যাকেটজাত মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছেন। ইতালির কাস্টমসে কাস্টমস্ অফিসারের সাথে তা নিয়ে চলছে বাকবিতন্ডা। কাস্টমস কর্মকর্তাকে তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারছেন না যে, প্যাকেট খুললে মিষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। কাস্টমস অফিসারের ভাঙাচোরা চেহারার বর্ণনা আমাদেরকে রসগোল্লা খাওয়ার আগে রসে মজিয়ে ফেলে। তাছাড়া ঝান্ডুদার পোশাক ব্যাগের উপরে বিভিন্ন দেশের কাস্টমসের সিল সব কিছুতে রসের প্রাচুর্য আছে। সেখানে নানা হাস্যরসাত্মক কান্ড ঘটানোর পরেও ঝান্ডুদাকে মিষ্টির প্যাকেট খুলতে হয়। কিছু বুঝে উঠার আগেই ঝান্ডুদা ক্ষেপে রসগোল্লা নিয়ে চুঙ্গিওয়ালার নাকে-মুখে লেপে দেয়। আর সবাইকে রসগোল্লা খেতে দেয়। রসগোল্লার রসে মজে ফরাসি উকিল আড়াই মিনিট চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। সবাই রসগোল্লার রসে মজে আবার রসগোল্লা খেতে চায় কিন্তু ততোক্ষণে তা শেষ। এই রম্য রচনার প্রতিটি চরিত্র আমাদের পেট ফাটিয়ে হাসায়।
ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখিতে জড়িয়ে পড়েন, শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় হাতে লেখা বিশ্বভারতী পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি সত্যপীর, রায়পিথোরা, ওমর খৈয়াম, টেকচাঁদ, প্রিয়দর্শী ইত্যাদি ছদ্মনামে আনন্দবাজার, দেশ, সত্যযুগ, শনিবারের চিঠি, বসুমতী, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখতেন। এছাড়া মোহাম্মদী, চতুরঙ্গ, মাতৃভূমি, কালান্তর, আল-ইসলাহ্ প্রভৃতি সাময়িক পত্রেরও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বই আকারে তাঁর মোট ত্রিশটি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো- দেশে-বিদেশে, জলে-ডাঙায়, উপন্যাস অবিশ্বাস্য, শবনম, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী এবং ছোটগল্প চাচা-কাহিনী, টুনি মেম প্রভৃতি।’পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ তাঁর আরেকটি অনবদ্য বই।
‘বই কিনে কেউ কখনও দেউলিয়া হয় না’ এই কথাটি কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে ১৯৪৯ সালে তিনি অর্জন করেন নরসিং দাস পুরস্কার। এ ছাড়া ১৯৬১ সালে অর্জন করেন আনন্দ পুরস্কার। গীতা তার সম্পূর্ণ মুখস্ত ছিল। এমনকী রবীন্দ্রনাথের গীতিবিতানও টপ টু বটম ঠোঁটস্থ ছিল তার। একবার এক অনুষ্ঠানে এক হিন্দু পুরোহিত গীতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছিলেন। সেই সভায় সৈয়দ মুজতবা আলী উপস্থিত ছিলেন। দূর্ভাগ্যক্রমে সেই পুরোহিত যে সব রেফারেন্স গীতা থেকে সংস্কৃত ভাষায় দিচ্ছিলেন তাতে কিছু ভুল ছিল। অবশেষে তিনি দাঁড়িয়ে সবাইকে হতবাক করে দিয়ে উনার সমস্ত রেফারেন্স মূল সংস্কৃত ভাষায় কি হবে তা সম্পূর্ণ মুখস্থ বলে যান।
তাঁর জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা বলতে যা বোঝায় সেটা কখনোই ছিল না। তিনি কখনও চাকরি করেছেন, কখনো লিখে টাকা আয় করেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘’মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক চাকুরি চেয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক কারণে তখন তাঁদের চাকুরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। আনন্দবাজার গ্রুপও তাঁকে চাকুরি দেননি। পরে, শান্তিনিকেতনে মুজতবার চাকুরি হয়”। শুধুমাত্র কলমকে ভরসা করে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ সালের অগাস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত, হালভাঙা নৌকোর মত কোনোক্রমে নিজেকে চালিয়েছেন।
তাঁর শেষ জীবনটা কেটেছে খুব কষ্টে। অমিতাভ চৌধুরী ১৯৯৩ সালে একটি লেখায় লিখছেন, ‘’সৈয়দদাকে শেষ দেখি কলকাতায় তাঁর পার্ল রোডের বাড়িতে। সুশীলা আসার নামে শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন ছাত্রী কিছু গুজরাতি আচার দিয়েছিলেন… ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে আচারের শিশি দিতে গিয়ে সৈয়দদার চেহারা আর পোশাক দেখে আমি অবাক। ছেঁড়া গেঞ্জি, নোংরা পাজামা এবং দিন তিনেক অন্তত দাড়ি কামানো হয়নি। সুপুরুষ মানুষের এই অবস্থা। আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল।’’ এর পরে অনেক কথা হয় দু’জনের। আলী সাহেব তখন কাশছেন ঘন ঘন। ‘কিন্তু কথায় কোনও ছেদ নেই।’ আড্ডা দিতে দিতেই বলেছিলেন, ‘দর্পহারী মধুসূদন একে একে সব কেড়ে নিচ্ছেন আমার। হাতের কলম সরে না, লিখতে কষ্ট হয়, আর না লিখতেই যদি পারি, তবে বেঁচে কী লাভ?’
তাঁর অনেক বক্তব্য সম্পর্কে মতান্তর আছে, তাতে কি আসে যায়? কোন প্রাবন্ধিক অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করতে পারেন? তাঁর রচনার পর থেকেই তথাকথিত প্রাবন্ধিকদের দুর্বোধ্য, কষ্টকল্পিত বাক্যের রচনা পাঠকরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। যথার্থ পণ্ডিতেরাও এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন, শুধু নিজের বিষয়ের ওপর দখল থাকাই বড় কথা নয়, সাবলীল ভাষায় তা প্রকাশ করতে না জানলে লেখক হওয়া যায় না।