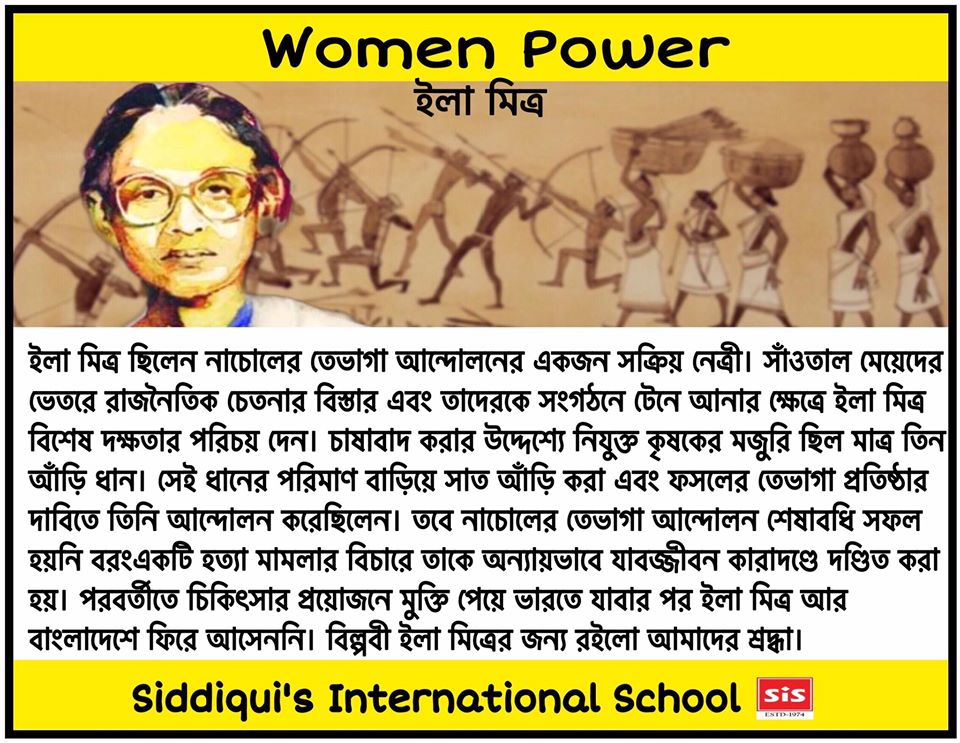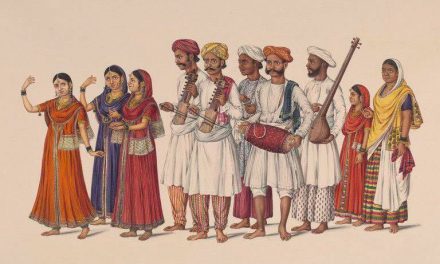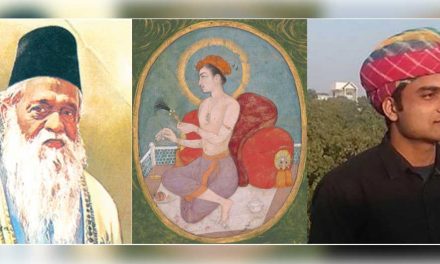বিবাহসূত্রে ১৯৪৫ সালে কলকাতার মেয়ে ইলা মিত্রকে চলে আসতে হয় চাঁপাই নবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুরে। পরবর্তী সময়ে পরিবারের শ্রেণি-অবস্থানকে অতিক্রম করে, কমিউনিস্ট নেতা ও স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্র এর সঙ্গে, তিনি যুক্ত হন জমিদারি উচ্ছেদ ও জোতদারি শোষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ের আন্দোলনে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের উপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলার ১৯টি জেলায় গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন। তেভাগার দাবিতে রাজশাহী জেলার, বিশেষভাবে নাচোলের কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ইলা মিত্র অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে তাঁর এতটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে, তারা তাঁকে শুধু বিশ্বাসই করতেন না, সে সঙ্গে নিজেদের একজন বলেও ভাবতেন। ইলা মিত্র ক্রমশ হয়ে ওঠেন সাঁওতাল ও অন্যান্য কৃষকদের ‘রাণীমা’। সাঁওতাল মেয়েদের ভেতরে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার এবং তাদেরকে সংগঠনে টেনে আনার ক্ষেত্রে ইলা মিত্র সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। বরেন্দ্র এলাকায় প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশ আড়ি (কাঠা/ ধামা) ধান কাটা ও মাড়ানোর জন্য জমিতে চাষাবাদ করেছেন যে কৃষক বা ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মজুর পেতেন তিন আড়ি ধান। ঐ ধানের পরিমাণ বাড়িয়ে সাত আড়ি করা এবং ফসলের তেভাগা প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁর ভূমিকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে তা জায়গা করে নিয়েছে কালোত্তীর্ণ স্থানীয় লোকগীতিতে। তবে নাচোলের তেভাগা আন্দোলন শেষাবধি সফল হয়নি। কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষে দারোগাসহ চারজন পুলিশ নিহত হওয়ার সূত্রে পাকিস্তানি শাসকবর্গ আদিবাসীদের ওপর প্রচন্ড নিপীড়ন চালাতে শুরু করলে নাচোলের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। ইলা মিত্র নিজে চরম লাঞ্ছনার শিকার হন, এ ছাড়া তাঁকে এক নম্বর আসামি করে অনিমেষ লাহিড়ী, বৃন্দাবন সাহা, শেখ আজাহার হোসেনসহ মোট ৩১ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা রুজু করা হয় এবং বিচারে ইলা মিত্রসহ ২৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। তবে তাঁর মুক্তির দাবিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সহ বিভিন্ন মহল সোচ্চার হন। নাচোলে সরকারি বাহিনীর নির্যাতনের বিষয়টি পূর্ব বাংলার সংসদে উত্থাপনের চেষ্টা মুসলিম লীগ সরকার প্রতিহত করে। তবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় হীরেন মুখার্জী ইলা মিত্রের বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কলকাতা যাবার পর ইলা মিত্র আর পূর্ব বাংলায় ফিরে আসেননি।
হরিনাথ, কাঙাল (১৮৩৩-১৮৯৬) সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বাউল গান রচয়িতা। তাঁর প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার, কিন্তু কাঙাল হরিনাথ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। কাঙাল ফিকিরচাঁদ বা ফিকিরচাঁদ বাউল নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ১৮৩৩ সালে নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালি গ্রামে তাঁর জন্ম।
শৈশবে স্থানীয় ইংরেজি স্কুলে হরিনাথের লেখাপড়া শুরু হয়, কিন্তু আর্থিক কারণে তা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ১৮৫৫ সালে বন্ধুদের সহায়তায় তিনি নিজ গ্রামে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামের সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরের বছর তাঁরই সাহায্যে কৃষ্ণনাথ মজুমদার কুমারখালিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।
গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য এবং তাদের শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে হরিনাথ সারাজীবন আন্দোলন করেছেন। অত্যাচারিত এবং অসহায় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লিখতেন, পরে ১৮৬৩ সালে তিনি নিজেই গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক ও শেষে এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এতে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও কৃষকদের প্রতি তখনকার নীলকর ও জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হতো। ফলে ব্রিটিশ সরকার এবং স্থানীয় জমিদারদের পক্ষ থেকে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যান। এসব কারণে পত্রিকাটি তখন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।
হরিনাথের জীবনে কখনও সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি ১৮৭৩ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যে দীর্ঘ ১৮ বছর পত্রিকা প্রকাশের পর আর্থিক কারণে এবং সরকারের মুদ্রণ শাসনব্যবস্থার কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে হয়।
হরিনাথ ছিলেন ফকির লালন শাহর শিষ্য। তিনি অধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ১৮৮০ সালে ‘কাঙাল ফিকির চাঁদের দল’ নামে একটি বাউল দল গঠন করেন। বাউল গানের ক্ষেত্রে হরিনাথের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বহুসংখ্যক বাউল গান রচনা করেন এবং সেগুলি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি সহজ ভাষায় ও সহজ সুরে গভীর ভাবোদ্দীপক গান রচনা করতেন এবং সেগুলি সদলে গেয়ে বেড়াতেন। গানে ‘কাঙাল’ নামে ভণিতা করতেন বলে এক সময় কাঙাল শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ‘হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে’ তাঁর একটি বিখ্যাত গান। ১২৯০-১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে তিনি কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী নামে ১৬ খন্ডে বাউল সঙ্গীত প্রকাশ করেন। হরিনাথ শুধু গানেই নয়, গদ্য ও পদ্য রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন।
সাহিত্যচর্চায় হরিনাথের শিষ্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেন্দ্রনাথ রায় এবং জলধর সেন পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। হরিনাথের মোট গ্রন্থ ১৮টি। তন্মধ্যে উলেখযোগ্য কয়েকটি হলো: বিজয়বসন্ত (১৮৫৯), চারুচরিত্র (১৮৬৩), কবিতাকৌমুদী (১৮৬৬), বিজয়া (১৮৬৯), কবিকল্প (১৮৭০), অক্রূর সংবাদ (১৮৭৩), সাবিত্রী নাটিকা (১৮৭৪), চিত্তচপলা (১৮৭৬), কাঙালের ব্রহ্মান্ডবেদ (১৮৮৭-৯৫), মাতৃমহিমা (১৮৯৬) ইত্যাদি। মৃত্যুর পর তাঁর রচনাসমগ্র হরিনাথ গ্রন্থাবলী (১৯০১) নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ সালের ১৬ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।
ইলা মিত্র। বিবাহসূত্রে ১৯৪৫ সালে কলকাতার মেয়ে ইলা মিত্রকে চলে আসেন চাঁপাই নবাবগঞ্জে। সেখানে কমিউনিস্ট নেতা এবং স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে তিনি জমিদারি উচ্ছেদ ও জোতদারী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের উপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলার গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন। তেভাগার দাবিতে রাজশাহী জেলার, বিশেষভাবে নাচোলের কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ইলা মিত্র অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে তাঁর এতটাই গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে, তারা তাঁকে শুধু বিশ্বাসই করতেন না, সে সঙ্গে নিজেদের একজন বলেও ভাবতেন। সাঁওতাল মেয়েদের ভেতরে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার এবং তাদেরকে সংগঠনে টেনে আনার ক্ষেত্রে ইলা মিত্র বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। বরেন্দ্র এলাকায় প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশ আড়ি (কাঠা/ ধামা) ধান কাটা ও মাড়ানোর জন্য জমিতে চাষাবাদ করেছেন যে কৃষক বা ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মজুর পেতেন তিন আড়ি ধান। ঐ ধানের পরিমাণ বাড়িয়ে সাত আড়ি করা এবং ফসলের তেভাগা প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তবে নাচোলের তেভাগা আন্দোলন শেষাবধি সফল হয়নি। কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষে দারোগাসহ চারজন পুলিশ নিহত হওয়ায় পাকিস্তানি শাসকবর্গ আদিবাসীদের ওপর প্রচন্ড নিপীড়ন চালাতে শুরু করে, যার ফলে নাচোলের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। ইলা মিত্রকে ১ নম্বর আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয় এবং বিচারে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। জেলখানায় থাকা অবস্থায় তিনি অসংখ্যবার চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কলকাতা যাবার পর ইলা মিত্র আর পূর্ব বাংলায় ফিরে আসেননি। সেখানে গিয়ে যিনি নিজেকে আরো উপযুক্ত করেন এবং মানুষের উন্নয়ন করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি পর পর চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে তিনি জনমত সংগঠিত করতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের জন্য এই মহিয়সী নারীকে আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি।